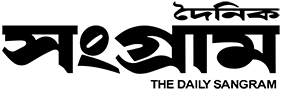কোনো জাতির স্বাধীনতাই সহজসাধ্য ছিল না বা হয়নি। কিন্তু আমাদের মত এতো চড়া মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা সমসাময়িক ইতিহাসে বিরল। কিন্তু আমরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম, এর সুফলগুলো আমরা আজও পুরোপুরি ঘরে তুলতে পারিনি বরং স্বাধীনতার প্রায় ৫৪ বছর পরেও স্বাধীনতার চেতনা অবাধ গণতন্ত্র, সাম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচার আজও আমাদের কাছে অনেকটাই অধরা। কাক্সিক্ষত সুশাসনের স্বপ্নও আজও আমাদের কাছে অপূরণীয় রয়ে গেছে। মহান স্বাধীনতার ব্যাপ্তি ও আমাদের প্রাপ্তির হিসেবটা এক জটিল সমীকরণেই আবর্তিত হচ্ছে। যা আমাদেরকে কোনভাবেই আশাবাদী করতে পারছে না। জুলাই বিপ্লবের পর জাতীয় জীবনে নতুন আশাবাদের সৃষ্টি হলেও রাজনৈতিক হানাহানি ও টেগ লাগানোর অপরাজনীতির কারণে তা নিয়েও সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।
বস্তুত, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ, নাগরিক সমাজের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি, আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন-এ তিনটি বিষয়ের ওপরই একটি জাতির ভবিষ্যৎ সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ভর করে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি বৈচিত্র্যময় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অর্জনও ভাল। কিন্তু গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণেই ম্লান হয়ে পড়েছে আমাদের সকল অর্জন। বিশেষ করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী আমলে তা একেবারে তলানীতে এসে ঠেকেছে। সঙ্গত কারণেই টেকসই উন্নয়ন ও গণমুখী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠার তাগিদও বেশ জোরালো। সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয় নিয়েও অনাকাক্সিক্ষত প্রশ্নের। তাই ব্যাহত হয়েছে সুশাসন। রাষ্ট্রও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারেনি। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সুশাসনের ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বিচ্যুতি আমাদেরকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পেছনে ফেলে দিয়েছে। আর স্বৈরাচারের পতনের পরও সে বৃত্ত থেকে এখনো বেড়িয়ে আসা সম্ভব হয়নি বরং পতিত ফ্যাসিবাদী অপশক্তি এবং তাদের দোসররা সক্রিয় থেকে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। তারা নতুন করে জনগণের টুটি চেপে ধরতে নানাবিধ অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।
শাসনকাজে দুর্বলতা থেকে উত্তরণের ভাবনা থেকেই সুশাসনের ধারণার সৃষ্টি। মূলত, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে বিশ্বব্যাংকের উপর্যুপরি ব্যর্থতার কারণেই ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সুশাসন বিষয়ক ধারণাটির উদ্ভব হয়। এটি বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন নামেও পরিচিতি লাভ করেছে। বস্তুত ‘সুশাসন’ একটি অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থা। তাই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ‘সুশাসন’ কথাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আধুনিক বিশ্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ১৯৯৫ সালে এডিবি এবং ১৯৯৮ সালে আইডিএ সুশাসনের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং সকল জটিলতা, বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।
কোনো সমাজ-রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিক অধিকারের বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়। আর সুশাসনের জন্য দরকার হয় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা। মূলত সুশাসন একটি দ্বিমুখী প্রত্যয়। প্লেটোর ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থে প্রথম এর ধারণা পাওয়া যায়। এখানে একপক্ষ জনগণ ও অন্যপক্ষ সরকার। সুশাসন নাগরিকদেরকে তাদের অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকগণ আশা-আকাক্সক্ষা, আবেগ-অনুভূমির অবারিত প্রকাশ ও সংবিধিবদ্ধ অধিকার ভোগ করতে পারে। শাসক-শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে রাষ্ট্রাচারও হয় গতিশীল ও সুশৃঙ্খল। বিষয়টির গুরুত্ব উপলদ্ধি করে আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বব্যাংক সুশাসনকে উন্নয়নের এজেন্ডাভুক্ত করে।
আইএমএফ-এর মতে, ‘দেশের উন্নয়নে প্রতিটি স্তরের জন্য সুশাসন আবশ্যক’। জাতিসংঘের ভাষায়, ‘সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন’। ম্যাককরনীর মতে, ‘সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়’। মূলত আইনের শাসন, মানবাধিকার সংরক্ষণ, শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক কাজে জবাবদিহিতা, সকল ক্ষেত্রে সমতা, সকলের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা, জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও জাতীয় শুদ্ধাচার সুশাসনের নিয়ামক ও চালিকা শক্তি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য মোটেই আহামরি নয় বরং পশ্চাদপদই বলতে হবে।
একথা ঠিক যে, আর্থ-সমাজিক নানা সূচকে বাংলাদেশ উন্নতি করেছে। কিন্তু সুশাসন, মানবাধিকার ও নৈতিকতার সূচকে পিছিয়ে পড়েছে বলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মহল থেকে জোরালো প্রশ্ন উপস্থাপন করা হচ্ছে। বস্তুত, এসব সূচকে উন্নতি করতে হলে গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বাংলাদেশ নানা ক্ষেত্রে, নানা সূচকে বিশ্বে ইতিবাচক অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে বলে দাবি করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পতিত স্বৈরাচার আমলে সুশাসন এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা একেবারে তলানীতে এসে ঠেকেঠিলো। যদিও জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে সে অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।
মূলত, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রশ্নাতীত না হওয়ার কারণেই সুশাসন ও মানবাধিকার বিষয়ে সাফল্যটা আমাদেরকে আশাবাদী করতে পারেনি। কারণ, বিদ্যমান ব্যবস্থায় জনগণকে শাসনকাজে সম্পৃক্ত করা যায়নি। আর গণসম্পৃক্ততাহীন রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো কখনো সর্বজনীন হয়ে ওঠেনা। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হলো জনগণ। সপ্তদশ শতক থেকেই আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি অলঙ্ঘনীয় বাস্তবতা। নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় সরকারে প্রতিনিধি বাছাইও করা হয়। আর এটিই আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের প্রথাগত অনুসঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।
আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের সংবিধিবদ্ধ পন্থা হচ্ছে নির্বাচন। গ্রিসের এথেন্সে গণতন্ত্রের আদি চেহারায় নির্বাচনকে যেভাবে ব্যবহার করা হতো এখন সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। অতীতে নির্বাচনকে শাসকগোষ্ঠীর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সে অবস্থার বিচ্যুতি ঘটেছে। সংকীর্ণতা ও আত্মকেন্দ্রীকতা সে অবস্থায় ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছে। ফলে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে জনমতের গুরুত্ব ও গণতন্ত্রের স্বরূপও ভিন্নতর।
তবে আধুনিক ধারার না হলেও গণরায়ের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ঐতিহ্য প্রাচীনই বলা যায়। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগ ছিল সীমিত আকারে। পুরো মধ্যযুগেও রোমান সম্রাট ও পোপের মত শাসক বাছাই করতেও নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। তবে আধুনিক ‘নির্বাচন’ হলো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সরকার নির্বাচন। সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপে যখন প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের ধারণা এলো তার আগে জনসাধারণকে দিয়ে সরকারি পদাধিকারী বাছাইয়ের এই আধুনিক ‘নির্বাচন’ বিষয়টির আবির্ভাবই হয়নি।
গণতন্ত্রের অভিযাত্রা বেশ পুরনো হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে কোম্পানী শাসনের অবসান ও ভারত বিভাজনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে আধুনিক গণতন্ত্রের সূচনা হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারত একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয় এবং একটি নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার কারণেই স্বাধীনতার পর ভারতের ব্যাপক অগ্রগতি। ফলে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু একই সময়ে স্বাধীনতা লাভ করলেও গণতন্ত্র চর্চায় পাকিস্তান তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি।
এক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ভোটের প্রথা রহিত করে ইলেকট্রোরাল কলেজ প্রথা সৃষ্টি করা হয়। ১৯৬২ সালে এ পদ্ধতির ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় এবং প্রাদেশিক সংসদের সদস্যদের নির্বাচিত হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে নির্বাচনের গণরায়ের প্রতি পাক শাসকচক্র শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতে পারেননি। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র আর অখন্ড থাকতে পারনি। ফলে এক অনিবার্য বাস্তবতায় ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ নামের নতুন এক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে।
আমাদের স্বাধীনতার অন্যতম চেতনাও ছিল উদার গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রেই সুশাসন নিশ্চিতকরণ। কিন্তু সে লক্ষ্য আমাদের কাছে আজও অনেকটাই অধরা। আমাদের দেশের গণতন্ত্র চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ঠিক তেমনিভাবে সুশাসনের সূচকেও আমারা অনেকটাই পিছিয়ে। গণতন্ত্রকে নির্বিঘ্ন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে অনেকবারই রাজপথে নামতে হয়েছে। এজন্য আমরা বেশ মূল্যও দিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যও এসেছে। কিন্তু অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতা আমরা রক্ষা করতে পারিনি। ফলে আমাদের গণতন্ত্রের সঙ্কটও কেটে যায়নি; সুশাসনের ভিত্তিও মজবুতি পায়নি। সংবিধানে গণতন্ত্রকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এর প্রায়োগিক দিক এখনও বিতর্কমুক্ত নয়। এ বিষয়ে ফ্যাসিবাদী তথাকথিত গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। তখনও সংবিধানে গণতন্ত্র ছিলো, মেয়াদান্তে নির্বাচনও হয়েছে। কিন্তু সে গণতন্ত্র ও নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন ছিলো না। গণতন্ত্রের নামে যা হয়েছে তা ছিলো পুরোপুরি তামাশা ও ভাঁওতাবাজি।
পতিত ফ্যাসিবাদী আমলে সুশাসনের বিচ্যুতি ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে নাগরিকরা থাকেছে অধিকার বঞ্চিত। ফলে সে সময় নুসরাত, তনু ও সাগর-রুনীরা মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের স্বীকার হয়েছেন। এসব হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে স্বজনরা বিচারের প্রহর গুণলেও তা তাদের কাছে অধরাই থেকে গেছে। মূলত, ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রমাণ হয় রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রতি অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই। তাই রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের হতাশা ও উদ্বেগ বেড়েছে। ফলে জুলাই বিপ্লব ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদের দৃশ্যপট থেকে বিদায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো।
আওয়ামী বাকশালী আমলে দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়ে এসব অভিযোগের পরিসরটা ছিলো একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের। বিশেষ করে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যেভাবে হয়েছে তা গণতন্ত্র বা নির্বাচন বলার কোন সুযোগ ছিলো না। যা রাষ্ট্র, সরকার ও নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে একটা বড় ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক গেটেলের মতে, ‘গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কোন পর্যায়ে আছে তা বোঝা যায় নির্বাচকমণ্ডলী সরকারের উপর কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে ও সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে তার সম্বন্ধ কিরূপ তা থেকে’।
বস্তুত আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমুখী। এমন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যও হতে হবে গণমুখী। রাষ্ট্রকে কল্যাণকামী ও গণমুখী করতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। বিষয়টি অন্যান্য দেশের সংবিধানের মত আমাদের সংবিধানেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ বিষয়ে আমাদের সংবিধানে বেশ কিছু অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগটা একেবারেই গৌণ পর্যায়েই ছিলো। ফলে ফ্যাসিবাদী ও মাফিয়াতন্ত্রীরা জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিলো। আর তা স্থায়ী হয়েছিলো প্রায় ১৬ বছর।
যদিও আমাদের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র হলো সুশাসনের প্রাণ। তাই বলা হয় এ অনুচ্ছেদে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা (৫৯ অনুচ্ছেদ) ও এর ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ ৬০) সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেহেতু গণতন্ত্র মানেই জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নিশ্চিতের নিশ্চয়তা প্রদান। তাই এসব অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুশাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।
সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা হিসেবে ন্যায়পাল নিয়েগের এর বিধান যুক্ত করা হয়েছে। ১৮০৯ সালে সুইডেনে সর্বপ্রথম ন্যায়পালের বিধান জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে এ বিধান যুক্ত করা হয়। তবে এটি এখন পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটিকেও বড় ধরনের একটি অন্তরায় বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতাবানরা সব সময়ই বিষয়টি নিয়ে খুবই উদাসীন।
এছাড়া সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ২৬-৪৭) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এবং অষ্টমভাগে (অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২) সরকারি অর্থের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের জন্য মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় দেশে সুশাসন বাস্তবায়নে সকল প্রকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (Constitutional guarantee) আমাদের সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিষয়টি ইতিবাচক হলেও পশ্চাদপদ মানসিকতার কারণে এর সুফল আমরা ঘরে তুলতে পারিনি।
আমাদের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূলত ভঙ্গুর ও অস্বচ্ছ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে প্রধানত দায়ী করা হয়। এর সাথে যুক্ত আছে নানাবিধ অনুসঙ্গও। মূলত এসব কারণেই আমাদের দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেমন বিকশিত হয়নি, ঠিক তেমনিভাবে সুশাসনের সোনার হরিণও রয়ে গেছে আমাদের কাছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন পর্যন্ত দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন চালু ছিল। এরপর যখন সংসদীয় সরকার পদ্ধতি ফিরে আসলো তখন সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী Floor Crossing সমস্যা রয়ে গেছে। যা সুশাসনের অন্তরায় হিসেবে মনে করা হয়।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে পক্ষপাতদুষ্ট সংস্কৃতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, ভিন্নমতের ওপর দলন, পীড়ন ও নিপীড়ন, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার বিষয়টিও উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। তাছাড়া আইন প্রণয়নে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় না আনা, টেকনিক্যাল বিষয়গুলো খোলামেলা আলোচনা না করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত না করার ঘটনাও আমাদের দেশে সুশাসনের জন্য অন্তরায় মনে করা হয়।
এক্ষেত্রে একশ্রেণির রাজনীতিক ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এবং আইন মান্য করার ব্যাপারে উদাসীনতাও কম দায়ি নয়। এমন অভিযোগ জোরালো ভিত্তি পেয়েছে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের দেশের নির্বাচনগুলো পুরোপুরি অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে হচ্ছে না। আর নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তাহলে জবাবদিহিতার কোন ক্ষেত্রই অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় সুশাসন ধারণাটাও অসার হয়ে যায়। তাই সুশাসনের ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানে নিশ্চয়তা স্বত্ত্বেও শুধু মাত্র উদারনৈতিক গণতন্ত্র চর্চা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবেই আমরা এখনো ব্যর্থতার শৃঙ্খলেই আবদ্ধ রয়েছি। তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের আমাদেরকে এ সঙ্কীর্ণ বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে।
তবে জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন করে আশাবাদের সৃষ্টি হয়েছে। জাতির ঘাড়ে নতুন করে যাতে অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শক্তি জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসতে না পারে এজন্য অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য ৬ টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছিলো। গঠিত হয়েছিলো জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। কমিশনগুলোর প্রস্তাবনার ভিত্তিতে জুলাই ঘোষণা ও সনদ প্রণয়ন করা হয়েছে। আর এ সনদ বাস্তবায়ন করে ন্যায়-ইনসাফের নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য গণভোট অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই এতদবিষয়ক গণভোট অনুুষ্ঠিত হবে।
দুঃখের বিষয় হলো জাতির এ ক্রান্তিকালে রাষ্ট্রীয় সংস্কার ও জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পক্ষ বা মহল বিশেষ এখন পতিত স্বৈরাচারের মতই আচরণ করছে এবং তারা ফ্যাসিবাদী রেজিমে ফিরে যাওয়ার জন্য নানাবিধ কসরত চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি তারা জুলাই সনদ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গণভোটে ‘না’-এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু তাদের এ অবস্থান হবে গণবিচ্ছিন্ন হওয়ার অন্যমত অনুসঙ্গ ও আত্মঘাতি। তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং আগামী দিনে তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব ধরে রাখার জন্য সে নেতিবাচক বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না।
www.syedmasud.com