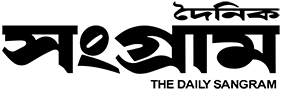মামলা ও আইনানুগ প্রক্রিয়া একটি স্বাভাবিক ও সভ্য সমাজের নিয়মিত একটি বিষয়। মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ, এবং নাগরিকদের বিপক্ষে সংঘটিত যে কোনো অন্যায় ও অপরাধ থেকে ন্যূনতম সুরক্ষা ও প্রতিকার পাওয়ার একটি মোক্ষম পন্থা হলো আইন ও বিচারাঙ্গন। কিন্তু বিগত সাড়ে ১৫ বছরের ফ্যাসিবাদী আমলে আওয়ামী লীগ বিচারিক প্রক্রিয়া অনুসরণের নামে কার্যত বিচারহীনতার সব আয়োজনই সম্পন্ন করেছে। আওয়ামী লীগ আমলে সাধারণ মানুষের অধিকার ব্যাপকভাবে ভুলুন্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এর বাইরে যা হয়েছে তাহলো বিচারের নামে প্রহসন। পুরো ১৫ বছরের শাসনামলে আওয়ামী লীগ বারবার আইন, আদালত ও বিচার মাধ্যমকে বিরোধী দলগুলোর নেতাকর্মীকে দমন করার কাজেই প্রয়োগ করেছে। আওয়ামী আমলে সম্পাদিত তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার এখন ইতিহাসের জঘন্যতম অবিচারের দৃষ্টান্ত হিসেবে সর্বজনবিদিত। কিন্তু আলোচিত এসব মামলা ছাড়াও আরো অনেকগুলো মামলার উদাহরণ দেয়াই যায়, যেগুলোকে বিচার বলা হলেও কার্যত তা কোনো বিচারই ছিল না; বরং ছিল প্রকৃত ভিকটিমকে প্রতারিত করার কৌশল।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিকভাবে যে মামলাটি দিয়ে বিরোধী দল বিশেষ করে জামায়াত-শিবিরের ওপর সবচেয়ে বড়ো ক্র্যাকডাউন চালিয়েছিলো তা হলো ফারুক হত্যা মামলা। ফারুক ছিলেন রাবির গণিত বিভাগের একজন ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী। ২০১০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী ফারুক হত্যার ঘটনা ঘটে বলে ধারণা করা হয়। পরদিন সকালে ফারুকের লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের একটি ম্যানহোল থেকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনাটি সে সময়ে বহু মানুষের ছাত্রজীবন ও সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দিয়েছিল। ঘটনাটি রাজশাহীতে হলেও আশপাশের সকল জেলায় দিনের পর দিন সাড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। শিবির জামায়াত সন্দেহে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। রাজশাহীর আশপাশের জেলাগুলো রীতিমতো পুরুষশূন্য হয়ে যায়।
শুধু তাই নয়, সারা দেশেই শিবিরের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউনের সূচনা হয়েছিল ফারুক হত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ এ ঘটনাকে জামায়াত-শিবির নিশ্চিহ্ন করার নিকৃষ্ট উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ঘটনার জেরে অবিশ্বাস্যভাবে ঢাকায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতাদের অভিযুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে এ হত্যার ঘটনাকে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের বিষয়টি উম্মোচিত হয়ে যায়। সে সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির নেতা শামসুল আলম গোলাপকে গ্রেফতার করে তার ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালানো হয়। তার মুখ দিয়ে প্রশাসন জামায়াত নেতাদের নাম বের করাতে চেয়েছিল। কিন্তু শামসুল আলম গোলাপ শত অত্যাচারের মুখেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন এবং চরম সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি মিডিয়ার সামনে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, “ওনারা জামায়াত করেন; বড়ো দলের কেন্দ্রীয় নেতা। তারা ঢাকায় থাকেন; তারা আমার মতো ক্যাম্পাসের একজন ছাত্রনেতাকে কেন ফোন দিবেন?” শিবির নেতা গোলাপের সে অদম্য সাহসিকতায় সে যাত্রায় আওয়ামী লীগের নোংরা পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।
তারপরও মামলার ইজাহারে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে জামায়াত শিবিরকে হয়রানি করার পথ উম্মুক্ত রাখা হয়। ২০১২ সালের ২৮ জুলাই পুলিশ ১,২৬৯ পৃষ্ঠার অভিযোগপত্র আদালতে দায়ের করে। মামলায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতাদেরও আসামী করা হয়েছিল। ২০১৯ জামায়াতের সাবেক নায়েবে আমীর আল্লামা সাঈদী রহ. ১০৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়। জামায়াতের সাবেক আমীর মাওলানা নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদকেও এ মামলায় প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৫-১৬ সালের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট নেতাদের ফাঁসি দিয়ে হত্যা করার কারণে তাদের নাম আর চূড়ান্ত অভিযোগপত্রে যুক্ত করা হয়নি। তবে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী তখনও জীবিত থাকায় তাকে অভিযুক্ত করা হয় ,এবং এ মামলার জেরে তাকে বেশ কয়েকবার এ মামলায় রাজশাহীতে হাজিরাও দিতে হয়।
সর্বশেষ আপডেট হলো- গত ১২ অক্টোবর রাজশাহী মহানগর দায়রা জজ প্রথম আদালত এ মামলার রায় ঘোষণায় সকল আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। এর মাধ্যমে নিরীহ মানুষগুলো অযাচিত অপরাধের দায় থেকে মুক্ত হলেন। নির্মম বাস্তবতা হলো, বিরোধী নেতাদের শায়েস্তা করার মানসিকতা ছিল বলেই আওয়ামী লীগ ফারুক হত্যা মামলার নির্মোহ তদন্ত করেনি। ফলে প্রতিহিংসাবশত: রাজনৈতিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা খালাস পেলেন ঠিকই কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা আড়ালে থাকার সুযোগ পেয়ে গেল।
একই ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাহের হত্যা মামলা নিয়েও। বহুল আলোচিত এ মামলায় দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ থাকলেও আপিল বিভাগের রায়ে মামলার বাস্তব চিত্রে ভিন্ন কিছু উঠে আসে। ২০০৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. তাহেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকাণ্ডের পরপরই রাজনৈতিক প্রভাব ও তৎকালীন পরিস্থিতির কারণে অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে শিবির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়। তবে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া শেষে আপিল বিভাগ জানিয়েছিল যে, হত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত বিরোধ, যা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা বা নীতিগত সিদ্ধান্তের অংশ নয়।
রায়ে আদালত আরও মন্তব্য করেন যে, মামলার প্রাথমিক তদন্তে রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তা মামলার অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক তাহের হত্যার ঘটনায় বিচারিক আদালতে দেয়া দুজনের মৃত্যুদন্ড উচ্চ আদালতেও বহাল রাখা হয়। তবে রায়ে বলা হয়, দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে কারও রাজনৈতিক বা সংগঠনভিত্তিক সংশ্লিষ্টতা অপরাধ সংঘটনের প্রধান কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়নি। মামলার নেপথ্য বিবরণীতে ভিন্ন একটি ঘটনাকে সামনে আনা হয়- যদিও এই ঘটনার সত্যতা নিয়েও নানা মহলে সংশয় রয়েছে।
মামলার চূড়ান্ত বিবরণীতে দাবি করা হয়, নিহত অধ্যাপক তাহের ও তার হত্যা মামলার প্রধান আসামী ড. মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন একই বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। অধ্যাপক তাহের শুধুমাত্র ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষকই ছিলেন না, একইসাথে শিক্ষকদের প্রমোশন সংক্রান্ত কমিটিরও সদস্য ছিলেন। তার মতামত ও সুপারিশ ছাড়া শিক্ষকদের প্রমোশন হওয়ার সুযোগ নেই, অন্তত তার বিভাগের শিক্ষকদের। অন্যদিকে, ড. মহিউদ্দিন ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক। তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে আবেদন করেছিলেন। আর অধ্যাপক তাহের ছিলেন ঐ কমিটিরই উল্লেখযোগ্য সদস্য। ড. মহিউদ্দিনের আবেদনটি নিয়ে যখন প্রোমোশন কমিটিতে আলোচনা হয়, তখন নিহত অধ্যাপক তাহের নিরব ছিলেন। তিনি প্রোমোশনের কোনো সুপারিশ করেননি। এখান থেকেই সংকটের সূত্রপাত হয়।
অধ্যাপক তাহেরের যুক্তি ছিল ৩টি। প্রথমত, ড. মহিউদ্দিনের চাকরির বয়স তখনও ১২ বছর পূর্ণ হয়নি যা অধ্যাপক হওয়ার জন্য অন্যতম শর্ত ছিল। তাছাড়া সহযোগী অধ্যাপক হিসেবেও তার ৫ বছর তখনো হয়নি। সবচেয়ে বড়ো কথা, অধ্যাপক তাহেরের মতে ড. মহিউদ্দিন প্রোমোশনের জন্য যোগ্য নন। কেননা, তার অধিকাংশ গবেষণাপত্রই যৌথভাবে করা। এককভাবে তার কোনো গবেষণা নেই বললেই চলে। আর একক গবেষণা ছাড়া অধ্যাপক পদে প্রোমোশন পাওয়ার সুযোগ নেই।
অধ্যাপক তাহের সুপারিশ না করায় ড. মহিউদ্দিন সংক্ষুব্ধ হয়ে প্রমোশন কমিটিকে পাশ কাটিয়ে সরাসরি ভিসির কাছে প্রোমোশন চেয়ে আবেদন করেন। নিজের দুর্বলতা আড়াল করার জন্য তিনি নিজের যৌথ গবেষণাকে এককভাবে করেছেন মর্মে দাবি করেন। তখন অধ্যাপক তাহের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান যে, ড. মহিউদ্দিন মিথ্যা বলছেন। তিনি এককভাবে ঐ গবেষণা করেননি। বরং একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুলতান উল ইসলামের সাথে মিলেই তিনি ঐ গবেষণাটি লিখেছিলেন। ফলশ্রুতিতে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ড. মহিউদ্দিনের প্রোমোশন প্রক্রিয়া স্থগিত করেন। শুধু তাই নয়, তার গবেষণাটি আসলে কার লেখা তা নির্ণয়ের জন্য একটি তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়। তখনই ড. মহিউদ্দিন ক্ষুব্ধ হয়ে যান এবং ক্রোধবশত অধ্যাপক তাহেরকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।
যদিও হত্যার পরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সময়ের ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহবুবে আলম সালেহীকে এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় এবং টানা কয়েকমাস রাজশাহীসহ অনেক জেলাতেই শিবিরের বিরুদ্ধে ক্র্যাকডাউন করে ঘটনাটিকে রাজনৈতিক কালার দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে, সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মাহবুবে আলম সালেহী পরবর্তীতে আদালত থেকেই বেকসুর খালাস পান। বাংলাদেশে বিগত ১৫ বছরে ফ্যাসিবাদী সরকার, দলীয় প্রশাসন ও নিজেদের মিডিয়া ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ শক্তিগুলোকে দমন করেছিল- এ ঘটনাগুলো এরই প্রমাণ। এ দীর্ঘ সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির যেভাবে প্রোপাগান্ডা ও রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হয়েছে তা সত্যিই নজিরবিহীন।
আরেকটি মামলার প্রসঙ্গ টেনে নিবন্ধটির সমাপ্তি টানছি। ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে আশুলিয়ার জনতা ব্যাংক শাখায় সংঘটিত ওই ডাকাতিতে এক নিরাপত্তাকর্মী নিহত হন এবং কয়েক লাখ টাকা লুট হয়। সে সময়ের ঢাকা রেঞ্জের পুলিশের তরফ থেকে তখন বলা হয়, এটি “শিবিরের সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের অংশ” এবং সংগঠনের রাজনৈতিক অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ ঘটনা ঘটানো হয়। ঘটনার পরপরই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলেও চূড়ান্ত তদন্তে দেখা যায়, ঘটনার সাথে ছাত্রশিবিরের কোনো সম্পৃক্ততাই নয়। বরং এটি ছিল ডাকাতির একটি ঘটনা। রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, “প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান, অভিযুক্তরা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে এই অপরাধ করেছে, সংগঠনের নির্দেশনা বা রাজনৈতিক আদর্শ এতে ভূমিকা রাখেনি।” রায়ের পর মানবাধিকার সংগঠন ও আইনি বিশ্লেষকেরা স্বীকার করেন যে, ঘটনাটির শুরুতে রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে যেভাবে সংগঠনটিকে দায়ী করা হয়েছিল, তা ছিল তদন্তের ন্যায্যতা ও নিরপেক্ষতার পরিপন্থী। এ রায়ে প্রমাণ হয়ে যায় যে, ছাত্রশিবিরের নাম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে জড়িয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছিল। এরকম দৃষ্টান্ত আরো অনেক মামলার রেফারেন্স দিয়েই প্রমাণ করা যায়। তবে লেখার ব্যাপ্তি বিবেচনায় এখানেই শেষ করছি।
পরিশেষে বলতে চাই, আওয়ামী লীগ বরাবরই নেতৃত্ব ও নেতার পরিবারের স্বার্থেই যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সঙ্গত কারণে দেখা যায়, দলীয় জনশক্তির সাথে সম্পৃক্ত মামলাগুলো নিয়ে তারা বরাবরই তামাশা করে। একজন মানুষ যেহেতু হত্যার শিকার হয়েছে, তাহলে কেউ না কেউ তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু কে হত্যা করলো তা বের করার চেয়ে আওয়ামী লীগ বরাবরই প্রতিপক্ষকে ফাঁসানো এবং রাজনৈতিক জিঘাংসা চরিতার্থ করাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই কারণে সাময়িকভাবে বিরোধী দলের নেতাকর্মীকে হয়রানি করা গেলেও চূড়ান্ত পরিসরে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায় আর প্রকৃত অপরাধীরা ধরাছোঁয়া আর বিচারের বাইরেই রয়ে যায়। বিচারের কথা বলে মুখে ফেনা তুললেও বাংলাদেশে বিচারহীণতা এবং প্রকৃত অপরাধীকে ছাড় দেয়ার রাজনীতি আওয়ামী লীগই বারবার করেছে; অন্তত ইতিহাস এমনটাই সাক্ষ্য দেয়।