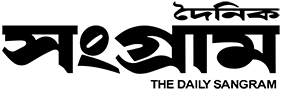গত সপ্তাহের পর
৪. সামরিক কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে পুলিশের এসপির মাধ্যমে রাজাকার নিয়োগ করা হবে।
৫. প্লাটুন পর্যায় পর্যন্ত রাজাকাররা সহজবোধ্য কমান্ড পদ্ধতি অনুসরণ করবে। প্লাটুন কমান্ডারদের বিশেষভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং ১৫ থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে একটি প্লাটুন গঠিত হবে।
৬. রাজাকাররা তাদের নিজ নিজ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশসহ অপরাপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করবে। প্রয়োজনবোধে বিদ্রোহী এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের কাজে তাদের তলব করা যেতে পারে এবং তারা তাদের নির্ধারিত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ করে পুল, কালভার্ট এবং বিদ্যুতের লাইন পাহারা দেবে। তথ্য সংগ্রহের কাজেও তারা নিয়োজিত থাকবে।
৭. কর্তব্যরত অবস্থায় রাজাকারদের সাথে অস্ত্র থাকবে। কর্তব্যশেষে নিম্নোক্ত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের অস্ত্র জমা দিতে হবে। অগ্রাধিকার- ১: নিকটবর্তী আর্মি/পুলিশ পোস্ট
অগ্রাধিকার- ২: নিকটবর্তী থানা
অগ্রাধিকার- ৩: রাজাকারদের যথাযথ পাহারায় ইউনিয়ন পরিষদ অফিস।
৮. অস্ত্রশস্ত্রের নিরাপদ হেফাজতের সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব জেলার পুলিশ সুপারের উপর ন্যস্ত থাকবে।
৯. রাজাকারদের চেনার সুবিধার্থে রাজাকাররা নীল রং এর আর্ম ব্যান্ড পরিধান করবে যার উপর বাংলায় লাল রং এ রাজাকার শব্দ লেখা থাকবে।
জুলাই মাসের প্রায় একই সময়ে ঢাকায় খ অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে তিনটি আদেশ জারি করা হয়। এর প্রথমটিতে লাইসেন্স বিহীন আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বারুদ বা বিস্ফোরক দ্রব্য রাখা নিষিদ্ধ করা হয় এবং লাইসেন্স করা আগ্নেয়াস্ত্র থানা কর্তৃপক্ষের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট এলাকার সামরিক কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতিক্রমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা আত্মরক্ষার জন্য ভ্রমণকালে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বহন করার অনুমতি দেয়া হয়।
দ্বিতীয় আদেশে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত, সরকারি স্থাপনার উপর হামলাকারী, আদালত গ্রাহ্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট পলাতক ব্যক্তিদের গ্রেফতারের ক্ষমতা রাজাকার ও জনসাধারণকে প্রদান করা হয়।
তৃতীয় আদেশে বলা হয় যে, ২ নং আদেশের অধীনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের পুলিশ অফিসার বা থানার অফিসার ইনচার্জের নিকট আনা হলে থানা কর্তৃপক্ষ অপরাধীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
রাজাকার গঠনের উপরোক্ত প্রক্রিয়ার পাশাপশি শান্তি কমিটি গঠনের একটি উদ্যোগও সরকারিভাবে গ্রহণ করা হয়। ২৫ মার্চ আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর সারা প্রদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচারে জনপদে হামলা চালায়। এরফলে নিরীহ মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে থাকে। আওয়ামী লীগ দলীয় এম এন এ, এমপিএ তথা জনপ্রতিনিধিদের বেশিরভাগই দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ায় এ দুর্দিনে তাদের পাশে থাকা, তাদের সান্ত্বনা দেওয়া এবং আর্মি নির্যাতন থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ দলীয় কোন লোক ছিল না। এ অবস্থায় পাকিস্তান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান এবং ৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের বিজয়ী সদস্য জনাব নূরুল আমিন, মুসলিম লীগের খাজা খয়ের উদ্দিন এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, জমিয়তে উলামা ইসলামসহ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও তাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে দুরাবস্থা থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন, তারা সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে গণহারে নির্যাতনের প্রতিবাদ জানান। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সামরিক বাহিনীর অপারেশন বন্ধ করা, সরকারের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান এবং সন্ত্রাস নৈরাজ্য রোধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শান্তি কমিটি গঠিত হয় এবং এ কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব প্রদান করা হয় মুসলিম লীগ নেতা খাজা খয়ের উদ্দিনের উপর। একই দলের অন্যতম নেতা এডভোকেট এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম এ কমিটির কোষাধ্যক্ষ, এডভোকেট নূরুল হক মজুমদার অফিস সম্পাদক, এবং পিপলস পার্টির মাওলানা নূরুজ্জামান প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটিও গঠন করা হয়।
এ কমিটিতে অধ্যাপক গোলাম আযম এবং জনাব আব্দুল খালেক ছিলেন জামায়াতের প্রতিনিধি। অন্যান্য যারা ছিলেন তাদের মধ্যে পিডিপির মাহমুদ আলী, কেএসপির আব্দুল জব্বার খদ্দর, নেজামে ইসলাম পার্টির মাওলানা সিদ্দীক আহমদ, মুসলিম লীগের ইউসুফ আলী চৌধুরী, ব্যারিস্টার আফসারুদ্দিন, আতাউল হক খান, লেবার পার্টির আব্দুল মতিন প্রমুখ। পরবর্তীকালে মে মাসের ২য় সপ্তাহে শান্তি কমিটি গঠনের সকল দায়িত্ব তৎকালীন সরকার গ্রহণ করেন এবং মহকুমা প্রশাসকরা সকল থানা ও ইউনিয়ন কাউন্সিলে শান্তি কমিটি গঠনের জন্য সার্কেল অফিসারদের নির্দেশ প্রদান করেন। এ ব্যাপারে মহকুমা প্রশাসকদের তরফ থেকে পরিপত্র জারি করা হয়। সেখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল যে, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সাথে বিভাগ, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত শান্তি কমিটি সমূহের গঠনতান্ত্রিক বা সাংগঠনিক কোন সম্পর্ক ছিল না, এটি - Hierarchical কোন প্রতিষ্ঠানও ছিল না এবং এ প্রেক্ষিতে অধঃস্তন কমিটির উপর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আবার কেন্দ্রীয় কমিটি জেলা, থানা বা ইউনিয়নে গঠিত কমিটি গুলোকে নির্দেশ দেয়ার কোন ক্ষমতাও সংরক্ষণ করতেন না। ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদেরকে আহ্বায়ক করে ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের মধ্যে ঐ সময়ে জামায়াতে ইসলামী সমর্থকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৬৫ সালে এবং ঐ সময়ে যারা চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের ৬০ ভাগ মুসলিম লীগ প্রায় ৩০ ভাগ আওয়ামলী লীগ সমর্থক এবং অবশিষ্টরা অন্যান্য দলের সমর্থক ছিলেন। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে অধ্যাপক গোলাম আযমের দাপ্তরিক কোন পদবি ছিল না। কোন প্রকার আদেশ নির্দেশ দেয়ারও কোন ক্ষমতা ছিল না। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে কোন বৈঠকে তাকে এ ধরনের কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতা দেয়ার সিদ্ধান্তও তৎকালীন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।
শাস্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল আইনশৃঙ্খলাসহ সমাজে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। পাকিস্তানকে অখন্ড রাখার জন্য এ কমিটি তৎকালীন সরকারকে সহযোগিতা করেছে সন্দেহ নেই। তারা অনেক ভাল কাজও করেছে বলে জানা যায়। জাতীয় লীগ প্রধান ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অলি আহাদ তার প্রণীত “জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫” শীর্ষক পুস্তকে যথার্থই বলেছেন যে, “শান্তি কমিটি যে কেবল মুক্তি বাহিনী বা বাংলাদেশ সমর্থকদের দমনে ব্যস্ত ছিল তাহা নহে। পাক বাহিনীর অকথ্য পাশবিক অত্যাচার ও লুণ্ঠন হইতেও দেশ বাসীকে রক্ষা করিতে আপ্রাণ সচেষ্ট ছিল। উভয় বাস্তবতাকে স্বীকার করাই হইবে সত্য ভাষণ,”
শান্তি কমিটির থানা ও ইউনিয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, এ কমিটি শুধু ইউনিয়ন কাউন্সিল কিংবা অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিদের প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি বরং সরকারের বিভিন্ন বিভাগও এজেন্সির প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কাজেও এ কমিটি ব্যবহৃত হয়েছে। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কাজে এ কমিটির সহায়তা নিয়েছেন। সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) কর ও ভূমি রাজস্ব আদায়ে এ ফোরামকে ব্যবহার করেছেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, চুরি ডাকাতি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে এ কমিটির সহযোগিতা নিয়েছেন। শান্তি কমিটির ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের সভাসমূহে উপস্থিত ব্যক্তিদের তালিকা এবং কমিটির কার্যবিবরণী পরীক্ষা করলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। এ কমিটিগুলো নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ দায়িত্বেই কাজ-কর্ম করেছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারকে সহায়তা করেছে। জামায়াতে ইসলামী অথবা অধ্যাপক গোলাম আযমের এক্ষেত্রে কোন ভূমিকা ছিল না এবং জনসাধারণের উপর অত্যাচার নিপীড়ন কিংবা মুক্তি বাহিনীকে দমনের জন্য তিনি এ কমিটিগুলোকে নির্দেশ দেয়ার এখতিয়ারও রাখতেন না।
শান্তিকমিটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী বাহিনীও ছিল না। এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার পর যে দলীল স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাতে সহযোগী বাহিনী সমূহের যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তাতে শান্তি কমিটির নাম ছিল না। এ বিষয়টি বাংলাদেশ ডকুমেন্টস ১৯৭১ পার্ট-৩ এর ২১৬ ও ২১৭ পৃষ্ঠা পরীক্ষা করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। এ ডকুমেন্টসটি ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।
১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ তারিখে আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর থেকে সংবাদ পত্রের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তৎকালীন অবজারভার হাউজে সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রেস লিয়াজো কর্মকর্তা মেজর সালেক নিয়মিত বসতেন এবং ঐ সময়ে সেন্সরশীপ ছাড়া কোন সংবাদ এমনকি সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় নিবন্ধও প্রকাশ করা যেত না। কোন কোন সময়ে সামরিক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধও লিখে - পাঠানো হতো। আমরা এ নিবন্ধগুলোকে সম্পাদকীয় আকারে প্রকাশ না করে চিঠিপত্র আকারে প্রকাশ করেছি বলে আমার এখনও মনে আছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের অত্যাচার নির্যাতন সম্পর্কে কোন রিপোর্ট প্রকাশ করতে দিতেন না। এমনকি তাদের সমালোচনামূলক কোন প্রতিবেদন বা নিবন্ধ লেখারও ক্ষমতা পত্রিকা সমূহের ছিল না। তবে ভারত বিরোধী যে কোন লেখা তাদের ছাড়পত্র ছাড়াই প্রকাশ করা যেত। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে কার্জন হলে সীরাতুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম আযম সামরিক সরকারের হত্যা নিপীড়ন ও নির্যাতনের কড়া সমালোচনা করেছিলেন। এ রিপোর্টটি পত্র পত্রিকাসমূহ প্রকাশ করতে পারেনি। কেননা এর আগেই তিনি এবং নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মৌলভী ফরিদ আহমেদের বক্তৃতা বিবৃতি প্রকাশের উপর এমবার্গো অর্থাৎ বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। দৈনিক পূর্ব দেশে আমরা নিয়মিত এমবার্গো রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ করতাম। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতার আর্মির সমালোচনামূলক বক্তৃতা বিবৃতি প্রকাশ না করার জন্য সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তার মধ্যে অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন অন্যতম প্রধান। পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাস তার রাজনৈতিক দর্শন ছিল। কিন্তু পাকিস্তানী বাহিনীর দমন-পীড়ন, হত্যা নির্যাতন ও লুটপাটের তিনি সর্বদা বিরোধীতা করছেন।
এখানে আরেকটি বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আর্মি প্রশাসন ১৯৭১ সালে অখন্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী পূর্ব পাকিস্তানী রাজনীতিকদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিহারী বলে পরিচিত অবাঙ্গালীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্থানে অপারেশন চালাতেন। এ অপারেশনে দলমত নির্বিশেষে সকল দল ও শ্রেণী পেশার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অসহযোগিতা চলাকালে অবাঙ্গালীদের উপর অনেক নির্যাতন-অত্যাচার হয়েছে। এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল জনতা তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং বহুলোককে হত্যা করেছে। আর্মি ক্র্যাকডাউনের পর তারা তার প্রতিশোধ নিয়েছে। পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর সদস্যরাও অবাঙ্গালী হওয়ায় অবাঙ্গালী বিহারীদের তথ্যকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছে এবং তার ভিত্তিতে নির্বিচারে অপারেশন চালিয়েছে। এ অপারেশনের শিকার মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপি ও কেএসপির নেতা কর্মীরাও ছিলেন। আর্মি ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ১৯৭১ সালে বিহারীরাও বিভিন্ন স্থানে প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ ও কর্মকান্ড চালিয়েছিল। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে মীরপুরে বসবাসকারী কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ) আমারই সহকর্মী অধ্যাপক রফিক উদ্দিন আহমদকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে তার লাশ টুকরো টুকরো করে কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। তিনি জামায়াতের নেতা ছিলেন এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রায়পুরা এলাকায় নির্বাচন প্রার্থী ছিলেন।
সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুট-পাট এবং ধ্বংসাত্মক তৎপরতা ছাড়াও ঐ সময়ে বামপন্থী, আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক দল এবং সন্ত্রাসী গ্রুপ গুলো বিশেষ করে চীন পন্থীদের জঘণ্য অপরাধী তৎপরতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। তাদের অপরাধ, অস্ত্র ও অনুপ্রেরণার উৎস ছিল পশ্চিম বাংলার চারু মজুমদারসহ নক্সালপন্থী দলগুলো। ভূস্বামী ও শ্রেণী শত্রু খতমের মাধ্যমে কৃষক শ্রমিকের একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েমের নামে আব্দুল হক, আব্দুল মতিন, আলাউদ্দিন, টিপু বিশ্বাস, মোহাম্মাদ তোয়াহা প্রমুখ চীন পন্থী কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুসারীরা ঐ সময়ের নৈরাজ্যকর অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে এবং নির্বিচারে বহু আওয়ামী লীগ নেতা এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তাদের হত্যা করে। কোন কোন সময় তারা মুক্তিবাহিনীকে তাড়া করে সেনা ক্যাম্পের দিকে নিয়ে যায়। ফলে তারা সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্মম হত্যার শিকার হয়। সর্বহারা দল, পূর্ব বাংলা কমিউনিষ্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (এম এলসহ বামপন্থী দল সমূহের নেতারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন না তারা মনে করতেন যে যদি স্বাধীনতা সংগ্রামকে অন্তত পাঁচ বছর পিছিয়ে নেয়া যায় তাহলে মানুষ শেখ মুজিবুর রহমানকে ভুলে যাবে এবং আওয়ামী লীগের পক্ষেও পশ্চিম বাংলাসহ ভারতের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বামপন্থী ও নক্সালেরা যে হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, এ ঐতিহাসিক সত্যটি এখন উপেক্ষিত হচ্ছে। এ হত্যাযজ্ঞের দায়ও জামায়াত এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর চাপানো হচ্ছে।
উপরোক্ত অবস্থায় আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ১৯৭১ সালে অধ্যাপক গোলাম আযম ও তার দলের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক, অপরাধমূলক নয়। তিনি এবং তার দল অখন্ড পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে এটা তার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল এবং তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চাননি। তিনি এ অঞ্চলের উপর ভারতীয় আধিপত্যও চাননি। তিনি দেশকে ভালবেসেছেন এবং দেশের মানুষকেও ভালবেসেছেন। এ প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে দেশের মানুষের উপর অত্যাচারে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সহযোগিতার অভিযোগটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি দেশ বিদেশে ইসলামী আন্দোলনের একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তিনি গোড়া আলেমও নন। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ একজন আধুনিক মানুষ। তাকে এবং তার দলকে রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অভিযোগের অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অন্যতম নেতা জনাব আহমদ শরীফের ডায়েরি নিয়ে জাগৃতি প্রকাশনী কর্তৃক ‘ভাব-বুদ্বুদ’ শিরোনামে প্রকাশিত পুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠায় জনাব আহমদ শরীফ এ অভিযোগের দার্শনিক পটভূমি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমি রাজাকারদের নিয়ে ঘাটাঘাটি নিরর্থক ও অন্যায় বলেই মানি, কেননা এক রাষ্ট্রপতি তাদের ক্ষমা করেছেন, অন্য এক জঙ্গী নায়ক জিয়া তাদের তার সহযোগী সম্বল করে রাজত্ব করেছিলেন। তখন কেউ আন্দোলন করেনি। সবাই উক্ত দুই শাসকের সিদ্ধান্তের বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসেনি যথাসময়ে। আমার লক্ষ্য ছিল গোলাম আযম কারণ আমার চোখে তিনি ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন একজন একটি ইসলামিক দলের সর্বজনমান্য নেতা ও ব্যক্তিত্ব, একটা রাজনৈতিক দলের একটি আদর্শের একটি লক্ষ্যের একটি প্রতিষ্ঠানের, একটি রাজনৈতিক ও শাস্ত্রিক শক্তির প্রতীক, প্রতীক ও প্রতিভু, তাই তার পতনে বা শাস্তিতে আমার ধারণা জামায়াতে ইসলমী দল হৃতবল, হীনবল হয়ে হয়ে আত্মবিলুপ্তি পেত।” (সমাপ্ত)