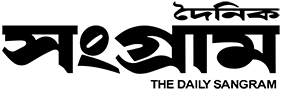দেশে আরো একটি ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ‘ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাংক।’ প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হবে, দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের সহজ শর্তে ঋণদান করা, যাতে তারা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারে। একই সঙ্গে যে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে তাদের অর্থায়ন করা। প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাংক সাধারণ মানুষের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারবে। বর্তমানে যেসব ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান আছে তারা সদস্যদের নিকট থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারলেও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করতে পারে না। প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাংকের ৬০ শতাংশ মালিকানা থাকবে দরিদ্র মানুষের হাতে। এ ব্যাংক ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এ ব্যাংক দেশের স্টক মার্কেটে তালিকাভুক্ত হতে পারবে না।
বর্তমানে দেশে ক্ষুদ্র ঋণদান করে নন-গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনগুলো (এনজিও) দেশের বিভিন্ন স্থান, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় এনজিওগুলোর ব্যাপক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং দরিদ্র মানুষগুলো নানা প্রয়োজনে এনজিওদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এনজিওগুলো সাধারণত জামানতবিহীন ঋণদান করে থাকে। তারা কার্যত ব্যক্তিগত গ্যারান্টির বিপরীতে ঋণদান করে থাকে। সাধারণ মানুষ উপায় না দেখে এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু এনজিওগুলোর প্রদত্ত ঋণের উপর সুদের হার অস্বাভাবিক রকম বেশি। কিন্তু তারা এমনভাবে ঋণের কিস্তি আদায় করে যাতে কারো বুঝার উপায় থাকেন না প্রকৃত পক্ষে তারা কত শতাংশ সুদ প্রদান করেন।
সর্বশেষ তথ্য মোতাবেক, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এনজিওগুলোর ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ২৪ শতাংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। কিন্তু কিছু এনজিও আছে তারা আরো উচ্চ হারে সুদ আদায় করে থাকে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, এনজিওদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে খুব কম মানুষই দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশী একজন অর্থনীতিবিদ ও গবেষক তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, এনজিও দের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে ৭ শতাংশ মানুষ টেকসইভাবে দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে আসতে সমর্থ হয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, এনজিওদের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে ৯ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে। তবে এদের মধ্যে অনেকেই আবার ভঙ্গুর অবস্থানে রয়েছে। তারা সামান্য অভিঘাতেই দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যেতে পারেন।
বর্তমানে সরকারি তালিকাভুক্ত ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হচ্ছে ৬৮৩টি। এর বাইরেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা সরকারি নিবন্ধনপ্রাপ্ত না হলেও ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ের হিসাব মোতাবেক, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন ৩ কোটি ২৩ লাখ জন। এদের মধ্যে ৯১ শতাংশই নারী। মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২ লাখ ৬৩ হাজার কোটি টাকা। এনজিওদের ঋণ আদায় কৌশল অত্যন্ত কঠোর। তারা গ্রুপ ভিত্তিক ঋণদান করে। এবং গ্রুপের কোন সদস্য চাইলেই কিস্তি না দিয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে বাধ্য হয়ে এক এনজিওর কিস্তি পরিশোধের জন্য অন্য এনজিও থেকে নতুন করে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো ক্রমাগত ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়ছে। ঋণ গ্রহণের পর একজন ব্যক্তি সে ঋণের অর্থ কিভাবে ব্যবহার করছে, তারা কী উদ্দিষ্ট কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহার করতে পারছে এসব বিবেচনা করা হয় না। এনজিওদের কাজ হচ্ছে দরিদ্র মানুষকে ঋণদান এবং নির্ধারিত সময়ে সুদ সমেত ঋণের কিস্তি আদায় করা। আগেকার দিনে কাবলিওয়ালারা যেভাবে গ্রামের মানুষকে ঋণদান করতো এবং কঠোরভাবে আদায় করতো তার সঙ্গে এনজিওদের ঋণদান ও কিস্তি আদায় প্রক্রিয়ার অনেকটাই মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্ন হলো, এতকিছুর পরও দরিদ্র মানুষ এনজিওর নিকট থেকে ঋণ কেন গ্রহণ করে? দরিদ্র মানুষগুলো প্রথাগত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ পান না। ঋণদানের ক্ষেত্রে জামানত প্রদানসহ যেসব শর্ত দেয়া হয় তা তাদের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব হয়না। তাই তারা এনজিওর নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে। সুদের হার এবং ঋণের কিস্তি আদায়ের ব্যবস্থা যত কঠিনই হোক না কেন।
নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এমন কিছু মানুষ বসে আছেন যারা সুযোগ পেলেই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এনজিওদের বিভিন্ন সুযোগ দিয়ে থাকেন। যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ঋণদান কার্যক্রম আছে যাকে ‘কৃষি ও পল্লি ঋণ’ নামে অভিহিত করা হয়। বিগত সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ঋণদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। এটি সাধারণ কৃষি ঋণ নয়। এ ঋণের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলা। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে ব্যবসায়রত সিডিউল ব্যাংকগুলোকে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিত। সে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তারা ঋণ মঞ্জুর ও ছাড়করণ করতো। ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ৫ লাখ টাকা থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণের সুদের হার প্রচলিত ব্যাংক ঋণের সুদের হারের চেয়ে এক শতাংশ কম। যেমন যখন ব্যাংক ঋণের সুদের হার ৯ শতাংশ নির্ধারিত ছিল তখন কৃষি ও পল্লি ঋণের সুদের হার ছিল ৮ শতাংশ। সিডিউল ব্যাংক থেকে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ গ্রহণ করতে চাইলে তাকে নানা ধরনের ডকুমেন্ট দিতে হতো। সম্পদ বন্ধক দিতে হতো। এসব ফর্মালিটিজ পালন করতে গিয়ে ১৬/১৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যেতো। ব্যাংকগুলো যদি এনজিও হোলসেল লিঙ্কেজে ঋণদান করতো তাহলে ঋণের কোন সর্বোচ্চ সীমা ছিল না।
তারা চাইলে ২০ কোটি ৩০ কোটি টাকা ঋণ দিতে পারতো। কোন ব্যাংক যদি ঋণদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারতো তাহলে অব্যবহৃত টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সুদবিহীন অ্যাকাউন্টে জমা রাখা হতো। পরবর্তী বছরে সে ব্যাংকের রেটিং খারাপ হতো। নতুন ব্র্যাঞ্চ খুলতে দেয়া হতো না। এনজিওগুলো সিডিউল ব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করতো তা উদ্যোক্তা বা তৃণমূল পর্যায়ে ২৪ শতাংশ সুদে বিনিয়োগ করতো। অর্থাৎ যে ঋণ পল্লি এলাকার উদ্যোক্তাদের ৮ শতাংশ সুদে পাবার কথা ছিল তা তারা পেতো ২৪ শতাংশ সুদে। প্রথম দিক এনজিওর মাধ্যমে মোট ঋণের কত শতাংশ বিতরণ করা যাবে তা নির্ধারিত ছিল না। পরবর্তীতে এনজিওদের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের হার কমিয়ে আনা হয়। বর্তমানে ৫০ শতাংশ ঋণ এনজিওদের মাধ্যমে এবং ৫০ শতাংশ ব্যাংকগুলোকে সরাসরি বিতরণ করতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য এনজিওদের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণের সুবিধা দেয়া হয়। ফলে এমন একটি সুন্দর উদ্যোগ উদ্যোক্তা উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখতে পারছে না।
দেশে ব্যাংকের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে। ফলে এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতা চলছে এ সেক্টরে। নানাভাবে ব্যাংকের সংখ্যা কমিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। একদিকে ব্যাংকের সংখ্যা কমানো অন্যদিকে নতুন ব্যাংক স্থাপনের উদ্যোগ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলতে পারে। তাই নতুন স্থাপনের চেয়ে বিদ্যমান ব্যাংকগুলোর সমস্যা সমাধানই এ মুহূর্তে বেশি প্রয়োজন। বিশেষ করে খেলাপি ঋণের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বমুখি প্রবণতা রোধ করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার শেষে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। এটা ব্যাংকগুলোর ছাড়কৃত ঋণের ৩৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। সেপ্টেম্বর কোয়ার্টার পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকগুলো মোট ১৮ লাখ ৩ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর ও ছাড়করণ করে। ২০০৯ সালে যখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে তখন দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে খেলাপি ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত সরকার আমলে সাড়ে ১৫ বছরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে ৬ লাখ ২১ হাজার ৫১৯ কোটি টাকা।
গত জুন মাসে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৬ লাখ ৮ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাত্র দিন মাসের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা। একই সঙ্গে বাড়ছে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ। সেপ্টেম্বর মাস শেষে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ৪৪ হাজার ২৩১ কোটি টাকা। জুন মাসের তুলনায় প্রভিশন ঘাটতি বেড়েছে ২৪ হাজার ৫১১ কোটি টাকা। ব্যাংক সব শ্রেণীর ঋণের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট হারে প্রভিশন সংরক্ষণ করে। প্রভিশন ঘাটতি থাকলে ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য ঋণ গ্রহীতাদের দেয়া ঋণের কিস্তি নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে না পারার কারণে অধিকাংশ ব্যাংকই বিনিয়োগযোগ্য তারল্য সঙ্কটে ভুগছে। তারা চাইলেও ঋণ আবেদনকারীদের চাহিদা মতো ঋণ দিতে পারছে না। দেশের ব্যাংকিং সেক্টর নানা জটিল সমস্যায় পতিত হয়েছে। এর মধ্যে সবার আগে উল্লেখ করতে হয় খেলাপি ঋণের কিস্তি আদায় করতে না পারার ব্যর্থতা।
বিগত সরকার আমলে অর্থমন্ত্রী হিসেবে আ হ ম মোস্তাফা কামাল দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, আজ থেকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক টাকাও বাড়বে না। তার এ আশ্বাসবাণী শ্রবণ করে অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংক সংশ্লিষ্টগণ আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী তার অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। খেলাপি ঋণের কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলেও অর্থমন্ত্রী এমনভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের বিদ্যমান আন্তর্জাতিক মানের আইনগুলো এমনভাবে পরিবর্তন করেন যাতে ঋণের কিস্তি আদায় না করেও কৃত্রিমভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেখানো যায়। একজন অর্থনীতিবিদ সরকারের এ উদ্যোগকে ‘কার্পেটের নিচে ময়লা রেখে ঘর পরিষ্কার দেখানোর’ প্রচেষ্টা হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু তার শেষ রক্ষা হয়নি। খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাড়তেই থাকে। বর্তমানে ব্যাংকিং সেক্টরে খেলাপি ঋণের উদ্বেগজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) কিছু দিন আগে তাদের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিল, খেলাপি ঋণের বিবেচনায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে।
অর্থনীতিবিদদের অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজমেন্ট লুকিয়ে রাখা খেলাপি ঋণ প্রকাশ্যে আনছে বলেই সার্বিকভাবে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেশি মনে হচ্ছে। আসলে এ ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ বিগত সরকার আমলে আইনি পরিবর্তনের মাধ্যমে যে খেলাপি ঋণকে আড়াল করা হয়েছিল সেগুলো তো আইন পুনঃপরিবর্তন করে প্রকাশে আনা হয়নি। ৫০০ কোটি টাকা এবং তারচেয়ে বেশি অঙ্কের খেলাপি ঋণ হিসাব পুনর্গঠন, ঋণ হিসাব অবলোপন, ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণকে ব্যাংকের মূল লেজার থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। মামলাধীন প্রকল্পের নিকট দাবিকৃত বিরাট অংকের খেলাপি ঋণকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। এসব আইনি পরিবর্তন বাতিল করা না হলে খেলাপি ঋণের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে না।
দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে সবচেয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে চলেছে খেলাপি ঋণ কালচার। কিন্তু কোন সরকার আমলেই খেলাপি ঋণের প্রবণতা রোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। খেলাপি ঋণ সমস্যা দূরীকরণের জন্য কার্যোত্তর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে খেলাপি ঋণ যাতে সৃষ্টি হতে না পারে। খেলাপি ঋণের জন্য আমরা সাধারণত ঋণ গ্রহীতাদের দোষারোপ করে থাকি। কথায় কথায় আমরা আমরা খেলাপি ঋণের জন্য উদ্যোক্তাদের দোষারোপ করে থাকি। খেলাপি ঋণ সৃষ্টির জন্য উদ্যোক্তা বা ঋণ গ্রহীতারা অবশ্যই দায়ী। কিন্তু পাশাপাশি অসৎ ব্যাংকারদের দায়ও কম নয়।
এ মুহূর্তে ব্যাংকিং সেক্টরে বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। নতুন ব্যাংক স্থাপন করে সমস্যাকে আরো জটিল করার কোন অর্থ থাকতে পারে না।
লেখক : সাবেক ব্যাংকার।