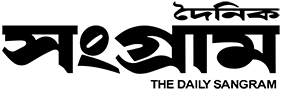মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী
বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণে ইসলামের প্রভাব প্রকটভাবে কাজ করেছে। এ অঞ্চলে ইসলামের আগমনের সূচনা হয় ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকেই। তবে আরব বণিকদের দ্বারা এ অঞ্চলে ইসলামের খবর ইতিপূর্বেই এসে যায়। সেসব বণিকের বাণিজ্য নৌ-জাহাজ সুদূর চীন-সুমাত্রা অঞ্চল পর্যন্ত যাতায়াত করতো বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর ছুঁয়ে। সেসব জাহাজে দূরপ্রাচ্যে ইসলাম প্রচার করতে যেসব সাহাবায়ে কিরাম যেতেন তাদের কেউ কেউ বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর এলাকায় সফর বিরতি দিয়ে এখানকার মানুষের সামনে ইসলামের সুমহান বাণী তু্লে ধরতেন। তারা বাংলাদেশের উপকূলীয় বন্দর ছাড়া ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পাননি সময়ের অভাবে। কারণ তাদের গন্তব্য ছিল দূরপ্রাচ্য। তখন চীন দেশ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য জগতজোড়া সুনাম ছিল। সেসব সাহাবায়ে কেরামের মাজার আজও চীনের ক্যান্টন নগরীর ম্যাসেঞ্জার মসজিদ প্রাঙ্গণে দেদীপ্তমান।
বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচারের সূচনা হয় ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ফারুকে আযম হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালের (৬৩৪-৬৪৪ খ্রি.) মধ্যভাগে। দলে দলে এখানে ইসলাম প্রচারক দল আসতে শুরু করেন। সরকারি পর্যায়ে আট শতকেই সর্বপ্রথম তদানীন্তন ভারতের সিন্ধু প্রদেশে ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন হয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভাতিজা ও জামাতা মুহাম্মদ বিন কাশিমের নেতৃত্বে। এরপর নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। এমনিভাবে ১২০৩ সালে মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ফলে এদেশে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এ সময় থেকে ক্রমাগত অব্যাহত গতিতে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল, আফগানিস্তান, ইরান, আরব ও তুরস্ক থেকে অসংখ্য মুসলমান বাংলায় আগমন করতে থাকেন। অধিকাংশই এসেছিলেন সৈনিক হিসেবে, অবশিষ্টাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য, ইসলাম প্রচার ও আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এভাবে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা হয়ে পড়েছিল ক্রমবর্ধমান। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, চতুর্থ প্রকাশ ২০০২, পৃ. ২১)।
১২০৩ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর থেকে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইংরেজদের হাতে বাংলার শেষ স্বাধীন ন বাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচশত চুয়ান্ন বছর বাংলাদেশ মুসলিম শাসনাধীন ছিল। এ সময়কালে একশত একজন বা ততোধিক শাসক বাংলায় শাসন পরিচালনা করেন। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ২৪)।
বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুসলিম প্রশাসনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার মদদ পায় এদেশের সান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে। হীন ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধনকুবের জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ, নন্দকুমার গং মীর জাফরকে সঙ্গে নিয়ে এদেশবাসীকে গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে সুযোগ করে দেয় বেনিয়া ইংরেজকে। এদেরই নিদারুণ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা শাহাদাত বরণ করেন। এ দেশের হিন্দু অধিবাসীরা নির্দ্বিধায় ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অন্যদের ওপর জমিদার, মহাজন, মালিক, মোক্তার বনে যায়। এদেরকে হাত করে নিয়ে ইংরেজ সরকার ক্রমান্বয়ে দিল্লির মসনদ দখল করে নিয়ে সারা ভারতের ওপর বিদেশী শাসন কায়েম করেন। পক্ষান্তরে এদেশের স্বাধীনতাকামী মুসলিম জনতা ভিনদেশীয় শাসকের বিরুদ্ধে বার বার আন্দোলন গড়ে তোলে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাসই আমাদের স্বাধীনতার চেতনার যথাযথ পরিচয় বহন করে।
একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ইংরেজদের গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করে বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে প্রথম অবতীর্ণ হন মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাংলার মানুষের- বিহারে সরকারি ডেপুটি গভর্নর রাজা রামনারায়ণ জায়গিরদার, রাজা সুন্দর সিংহ দেওয়ান আর খাজাঞ্জি, গঙ্গাবিষ্ণু, রাজা রাম নারায়ণের ভাই ধীরাজ নারায়ণ, গুপ্তচর বাহিনীর প্রধান মরলীধর, বিহারের জমিদার সেতার রায়, ভোজরপুরের সামন্তরাজা পালোয়ান সিং প্রমুখের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাংলার তিনি অকৃতকার্য হলেন বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে। ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বকসার রণাঙ্গনে ইংরেজ শক্তির নিকট চূড়ান্তভাবে পরাজয়বরণ করেন মীর কাশিম। অতঃপর পলাতক জীবনের দুঃসহ গুরুভার লাঘব করে বাংলার ১৭৭৭ সালের ৬ জুন দিল্লির আজমির গেটের সামনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মীর কাশিমের পরে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে এগিয়ে যান বাংলার গৌরব মজনু শাহ। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়কে কেন্দ্র করে রাজশাহী, রংপুর, বগুড়ার শিয়ালবাড়িয়া আর টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে ফকির বিদ্রোহের নেতা মজনু শাহ তার ঘোড়সওয়ার বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন ইংরেজদের ওপর। ফকির মজনু শাহকে লুণ্ঠনকারী আখ্যা দিয়ে ইংরেজরা যে জুলুম চালায়, ইতিহাসে তার নজির বিরল। মজনু শাহের পর এ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন সৈয়দ নেসার আলী ওরফে তিতুমীর। বাঁশবাড়িয়ায় তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার রণনিনাদে ইংরেজ শাসকদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। ১৮৩১ সালে একদিকে ইংরেজ বাহিনী আর অপরদিকে তাদের সহযোগী শক্তি খাসপুরের কৃষ্ণদেব রায়, গোবরডাঙ্গার কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায় প্রমুখের মুখোমুখি হয়েছেন কৃষক আন্দোলনের নেতা তিতুমীর। এ যুদ্ধে শহীদ হন তিতুমীর, শহীদ হন তার অসংখ্য অনুসারী। বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের আরেকটি চেষ্টা হলো ব্যর্থ। তিতুমীরের সেনাদল আর বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে যারা বেঁচে রইল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিচারালয়ে তাদের সকলেরই ফাঁসির হুকুম হয়।
তিতুমীরের এ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরও ইংরেজরা স্বাধীনতাকামীদের সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম হয়নি। এ জেহাদের পতাকা কাঁধে তুলে নেন তিতুমীরেরই অন্যতম সহযোগী ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া এবং জেহাদ আন্দোলনের বীর নায়কগণ। এসব স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর নায়কদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)-এর নেতৃত্বাধীন এ জেহাদি আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলার বীর সন্তান চট্টগ্রামের নূর আহমদ নিজামপুরী, নোয়াখালীর গাজী ইমামুদ্দিন, কুষ্টিয়ার কাজী মিয়াজান, মালদহের আহমদ বেলাল প্রমুখের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এ স্বাধীনতা আন্দোলনেরই পরিণত রূপ ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক এ সংগ্রামও পর্যুদস্ত হয় বিশেষ সম্প্রদায়ের সহযোগিতার কারণে।
১৯০৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহ অবহেলিত পূর্ব বাংলার উন্নয়নের জন্য বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব গ্রহণে সরকারকে সম্মত করান। কিন্তু বঙ্গভঙ্গে হিন্দু কায়েমি স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু করে দেয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদ করে হিন্দুদের শান্ত করে। বঙ্গভঙ্গ রদ ও বেঙ্গল প্যাক্ট ব্যর্থ হলে মুসলমানরা ক্রমে তাদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তার চিন্তা করতে বাধ্য হন। এ চিন্তারই ফসল ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাব উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে দু’টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও তদানীন্তন বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৪৭-এ দুই অঞ্চল মিলে একটি মাত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উপমহাদেশের দু’শত বছরের বাস্তবতাই যে লাহোর প্রস্তাবে প্রতিফলিত হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলল যখন ২৪ বছরের মাথায়ই লাহোর প্রস্তাবের মর্মানুসারে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র কায়েম হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৪৬-এর গণভোটরূপী নির্বাচনে বাংলাদেশের মুসলমানদের নিরঙ্কুশ রায়ের আলোকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়, জন্মলগ্ন হতেই সেই পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বাংলা বিদ্বেষী আন্দোলন শুরু করে দেয়। বিশেষ করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির মুখের ভাষা বাংলাকে জাতীয় জীবনে স্বীকৃতি না দেয়ার যে বিমাতাসুলভ আচরণ তারা প্রদর্শন করে, স্বাধীনতার ঊষালগ্ন হতেই তাতে এ দেশের মানুষের হৃদয়ে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও বিরাগ পুঞ্জীভূত হতে থাকে।
এ সময় গণপরিষদে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের পূর্বেই মানিঅর্ডার ফর্ম, ডাকটিকেট, মুদ্রা ইত্যাদি সরকারি মাধ্যমগুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি শুধু উর্দু ব্যবহার করে পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষাভাষীদের ভাষাগত অধিকার ও মর্যাদাদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই সে ১৯৪৭ সালের ১৮ মে মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলেমিনের উদ্যোগে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত উর্দু সম্মেলনে যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের জনৈক নেতা উর্দু ভাষাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সংকল্প ঘোষণা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ব্যাকডোর দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে ৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর তদানীন্তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবুল কাসেম এবং নুরুল হক ভূঁইয়া ‘তমুদ্দন মজলিস’ নামে একটি ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সে প্রতিষ্ঠান ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই মহান ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে তমুদ্দন মজলিসের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রথম প্রকাশ্য দাবি তোলে। প্রবীণ ইসলামি চিন্তাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আল্লামা আবুল হাশিম, ড. হাসান জামান, অধ্যাপক গোলাম আযম, অধ্যাপক শাহেদ আলী, অধ্যাপক আবদুল গফুর, সানাউল্লাহ নূরী, মাওলানা সাখাওয়াতুল আম্বিয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন আদর্শিক দায়িত্ব পালনের তাগিদেই।
ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়েই এদেশের স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীকার আন্দোলনে এবং সর্বশেষ যে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে, তার প্রতিটি স্তরেই লাহোর প্রস্তাবের মর্মবাণী বাস্তবায়নই ছিল মূল লক্ষ্য। আর লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি কোনো ইতিহাস সচেতন ব্যক্তিরই অজানা নয়। স্বাধীকার আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭০ সালে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে তার মেনিফেস্টোতে কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী কোনো আইন পালন না করার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে আওয়ামী লীগ স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিল, ‘৬-দফা বা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মসূচি ইসলামকে বিপন্ন করে তুলেছে বলে যে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে, সে মিথ্যা প্রচারণা থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা শেষবারের মতো আহবান জানাচ্ছি। অঞ্চলে অঞ্চলে এবং মানুষে মানুষে সুবিচারের নিশ্চয়তা প্রত্যাশী কোনো কিছুই ইসলামের পরিপন্থী হতে পারে না। আমরা এ শাসনতান্ত্রিক নীতির প্রতি অবিচল ওয়াদাবদ্ধ যে, কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামী নীতির পরিপন্থী কোনো আইনই এ দেশে পাস হতে বা চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না।’ (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও নির্বাচিত দলিল, নুহ-উল-আলম লেনিন সম্পাদিত, সময় প্রকাশন, ২০১৫, পৃ. ২৬৫)।
১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে বেতার ও টেলিভিশনে শেখ মুজিবুর রহমান একটি ভাষণ দেন। সে ভাষণে ‘লেবেলসর্বস্ব ইসলাম নয়’ অংশে তিনি বলেন, ‘আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য- লেবেলসর্বস্ব ইসলামে আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী, ইনসাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রসুলে করীম (সা:)-এর ইসলাম; যে ইসলাম জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বারবার যারা অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, লাঞ্ছনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছেন; আমাদের সংগ্রাম সেই মোনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান, সে দেশে ইসলামবিরোধী আইন পাসের ভাবনা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা শায়েস্তা করার জন্য।’ (বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, নভেল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২১)।
তাছাড়া আমরা লক্ষ্য করি, সব আন্দোলনেই ইসলামের প্রভাব সক্রিয় ছিল। যেমন- মওলানা ভাসানীর ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কারগারি সম্মেলনে পাকিস্তানকে বিদায় জানিয়ে ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলা, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমানের ‘ইনশাআল্লাহ’ বলা, ৯ মার্চ পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর ‘লাকুম দীনুকুম ওলিয়াদীন’ বলা, ৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রবাস থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন ইশতিহার ও নির্দেশাবলিতে ‘আল্লাহ আমাদের সহায়’, ‘নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব’ প্রভৃতি লেখার মাধ্যমে ইসলামের বৈপ্লবিক চেতনার প্রকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালে ১৪ এপ্রিল আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার মাত্র ৪ দিন পর প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশাবলি পত্র দেয়া হয়। এ নির্দেশাবলি পত্রের শীর্ষেই লেখা হয় ‘আল্লাহু আকবার’ তারপর স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করে বলা হয় ‘বাঙালির অপরাধ তারা অবিচারের অবসান চেয়েছে, বাঙালির অপরাধ তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততিদের জন্য অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার দাবি জানিয়েছে, বাঙালির অপরাধ আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট পৃথিবীতে আল্লাহর নির্দেশ মতো সম্মানের সাথে শান্তিতে সুখে বাস করতে চেয়েছে। বাঙালির অপরাধ মহান স্রষ্টার নির্দেশ মতো অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে এক সুন্দর ও সুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সংকল্প ঘোষণা করেছে। .... আমাদের সহায় পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য। মনে রাখবেন, আপনার এ সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম, সত্যের সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার দুশমন বাঙালি মুসলমান নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা কাউকে হত্যা করতে, বাড়ি-ঘর লুট করতে, আগুন জ্বালিয়ে দিতে এতটুকু দ্বিধা করেনি। মসজিদের মিনারে আজান প্রদানকারী মুয়াজ্জেন, মসজিদ গৃহে নামাজরত মুসল্লি, দরগাহ-মাজারে আশ্রয়প্রার্থী হানাদারদের গুলি থেকে বাঁচেনি।.... এ সংগ্রাম আমাদের বাঁচার সংগ্রাম। সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রেখে ন্যায়ের সংগ্রামে অটল থাকুন।
স্মরণ করুন! আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ‘অতীতের চাইতে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুখকর।’ বিশ্বাস রাখুন ‘আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।’ (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯-২২)।
উপরোক্ত নির্দেশাবলিটি ছিল সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে প্রবাসী সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম নির্দেশনামা। নির্দেশনামাটির শীর্ষে লেখা ছিল- ‘আল্লাহু আকবার’ এবং শেষ হয়েছিল এই বলে- ‘আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় নিকটবর্তী।’ এ নির্দেশনামা বিশ্লেষণ করলে ধর্মনিরপেক্ষতাতো নয়ই, বরং ইসলামের প্রতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাসের বিষয়টিই স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনা বলে স্বীকৃত হয়।
এ ছাড়াও স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রতিদিন পবিত্র কুরআন মাজিদ ব্যাখ্যা করে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করা হতো। এসব প্রেক্ষিতই বলে দেয় তিন লাখ মসজিদের এদেশ তার স্বাধীনসত্তা মূলত লাভ করেছে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রভাবে। এসবের পরও যদি কেউ বলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাই স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা, তবে তার চেয়ে হাস্যকর দাবি আর কী হতে পারে?
লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলেজ শিক্ষক।