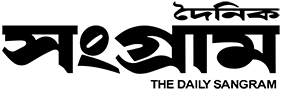দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের অন্যতম প্রধান মৌলিক উপাদান জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিরাট একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, সাবেক ক্ষমতাসীন ফ্যাসিস্ট দল আওয়ামী লীগ কর্তৃক দেশের জনসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তিকে বিভক্ত করার ফলে জাতীয় ঐক্যে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল সাম্প্রতিক সময়ে যুদ্ধাপরাধের নামে নতুন ইস্যু সৃষ্টি করে স্বাধীনতার ৩৯ বছর পর বানোয়াট অভিযোগে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের বিচারের নামে প্রহসন জাতিকে শুধু বিভক্তই করছে না, নতুন বিতর্কেরও সৃষ্টি করছে এবং দেশের ঐক্য, সংহতি এবং স্বাধীনতার ভিত্তিকেও দুর্বল করছে।
বিশ্লেষকরা মনে করেন, একটি প্রতিবেশী দেশ এ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার মাধ্যমে আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং দেশটিকে তার পণ্যের বাজার বানানোর যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় এই বিভেদ বিতর্ক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টির প্রয়াস কার্যত তারই একটি অংশ হয়ে যেতে পারে। তবে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, এ দেশেরই রাজনীতিকদের বিভ্রান্ত একটি দল জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের ব্যাপারে জন্য তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। ৫৩ বছর আওয়ামী লীগ তাদের দাসত্ব করেছে, এখন আরেকটি দল এ ব্যাপারে সক্রিয়া হয়ে উঠেছে।
বলাবাহুল্য এ প্রতিবেশী দেশটি ১৯৫ জন চিহ্নিত পাকিস্তানি সক্রিয় যুদ্ধাপরাধীকে বেকসুর খালাস দিয়ে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল এবং ৪৩ বছর পর ঐ অপরাধীদের বিচারের জন্য প্রণীত আইনে ভুয়া অভিযোগে এ দেশের বরেণ্য আলেম-ওলামা এবং আধিপত্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের প্রহসনমূ লোকারণ্য আলেম জনাব আধিপত্যবাদ বাংলাদেশে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে হত্যা করেছে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানউত্তর বাংলাদেশে বড় একটি রাজনৈতিক দল তাদের অপকর্ম লুকানো লক্ষ্যে নতুন করে যুদ্ধাপরাধের ধূয়া তুলে দেশের মানুষ বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।
অভিজ্ঞ মহলের মতে, একটি দেশকে কব্জা করার একাধিক পন্থা রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এবং অন্যটি হচ্ছে শত্রুর ঘরে আগুন লাগানো তথা সংঘাত-সংঘর্ষ ও হিংসা-বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিয়ে ঐক্য ও সংহতিকে ধ্বংস করে স্বার্থ উদ্ধার। বাংলাদেশ শেষোক্ত পন্থার শিকার বলে তাদের ধারণা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির ৮নং আদেশ নামে কথিত Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972 ১৯৭২ জারি করা হয়। এ আদেশটি দালাল আইন নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে যে সমস্ত লোক ব্যক্তিগতভাবে অথবা কোনও সংগঠনের সদস্য হিসেবে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীকে বাংলাদেশ ভূখণ্ড জবর-দখলে রাখার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে, তাদের দালালী করেছে, হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন, শিশু, মহিলাসহ সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন পরিচালনা, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস কিংবা বেসামরিক জনগণের সম্মান ও সম্পত্তির ওপর আঘাত হানা ও হানাদার বাহিনীকে অবৈধভাবে বাংলাদেশ দখলে রাখার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে কিংবা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা যুদ্ধ পরিচালনায় সক্রিয় সাহায্য করেছে তাদের বিচারই ছিল এ আইনের লক্ষ্য।
এ আইনে Collaborator বা দালালের একটি সংজ্ঞাও দেয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল- ‘Collaborator’ means a person who has i) participated with, aided or abetted the occupation army in maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by such army; ii) rendered material assistance in any way whatsoever to the occupation army by any act whether by words, signs or conduct iii) waged war or abetted in waging war against the Peoples Republic of Bangladesh. iv) actively resisted or sabotaged the efforts of the people and the liberation forces of Bangladesh in their liberation struggle against the occupation army; v) by a public statement or by voluntary participation propagandas within and outside Bangladesh or by association in any delegation or committee or by participation in purported by elections attempted to aid or aided the occupation army in furthering its design of perpetrating its forcible occupation of Bangladesh. `. দালালদের উপরোক্ত পরিচিতি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট।
বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন, শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন অথবা পাকিস্তানের অখন্ডতায় বিশ্বাস করতেন এ ধরনের রাজনীতিবিদ অথবা রাজনৈতিক দলসহ রাজাকার, আলবদর কেউই এ আইনের আওতাবহির্ভূত ছিলেন না। ১৯৭২ সালে দালাল আইন জারির পর ১৯৭৩ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে ১ লাখ লোককে গ্রেফতার এবং ৩৭৪৭১ জন রাজনৈতিক নেতাকর্মীকে দালাল হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের বিচারের জন্য ৭৩টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এ ট্রাইব্যুনালসমূহে প্রায় ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচার হয়। এদের মধ্যে দণ্ডিত হয় মাত্র ৭৫২ জন, অবশিষ্ট ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দালাল আইন জারি ও ভিন্ন মতাবলম্বী দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতাদের অভিযুক্ত করার পর থেকেই মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ প্রমুখসহ শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল ফজলের মতো শীর্ষ বুদ্ধিজীবীরা এর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় পুনর্গঠনের স্বার্থে কলাবরেটরদের ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে তাদের তরফ থেকে আবেদন ও দাবি উত্থিত হতে থাকে। দেশ গঠন ও পুনর্গঠনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন না করে সরকার সারাদেশে দালাল ও কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কাজে রত থাকায় তারা উষ্মা প্রকাশ করেন এবং জাতিকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে। তারা গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার এবং বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আহ্বান জানান এবং সকলের প্রতি ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দাবি করেন।
বলাবাহুল্য, দালাল আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আইনি সহায়তা পাবার পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে তৎকালীন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংস্থাসমূহের নেতাকর্মীরা সারাদেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আদালতে কোনও উকিল বা মোক্তার (মোক্তার পদটি বর্তমানে অবলুপ্ত) যাতে পক্ষভুক্ত না হয় সেজন্য তারা তাদের বাড়ি ও চেম্বারে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসতো। তথাপিও আদালতে তাদের পক্ষাবলম্বন করায় বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও থানায় দেড় শতাধিক উকিল লাঞ্ছিত হবার ঘটনাও ঘটেছে। এদিকে দালাল আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের (বেশির ভাগ আলেম ওলামা, মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক ও রাজনৈতিক কর্মী) অপরাধী চিহ্নিতকরণ ও তার অনুকূলে আলামত সংগ্রহের উদ্দেশে দেশব্যাপী তখন সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে প্রত্যেক থানায় একটি করে Fact finding Committee-ও গঠন করা হয়েছিল। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন থানার/ সার্কেলের ওসি/সিআই, আওয়ামী লীগের থানা সভাপতি, হেড কোয়ার্টার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রমুখ। তারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অপরাধ খুঁজতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছিলেন। কিন্তু শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে অপরাধ ও আলামত সংগ্রহে তারা ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় কারাগারে আটক বন্দীদের (যাদের বিরুদ্ধে কোনও অপরাধের প্রমাণ পাওয়া যায়নি) নির্দোষ গণ্য করে মুক্তি দেয়ার জন্য সার্কেল অফিসারদের তরফ থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অসংখ্য চিঠি প্রেরণ করা হয়। তৎকালীন সরকারের তরফ থেকে এর কোনও উত্তর বা তাৎক্ষণিক দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি।
এদিকে জাতীয় ঐক্য এবং সামাজিক ও পারিবারিক সংহতি ও সমঝোতার স্বার্থে দেশব্যাপী সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দাবিও জোরদার হতে থাকে। সরকার বিপাকে পড়েন। তার সামনে তখন দুটি পথ ছিল, এক. আইনী প্রক্রিয়ায় মামলার নিষ্পত্তি করা এবং অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দুই. ঐক্য, সংহতি ও সমঝোতার পথ অনুসরণ। সাধারণ ক্ষমাই ছিল এর উৎকৃষ্ট পন্থা। অবশেষে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির বাস্তবতা, নবলব্ধ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য গভীর ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের দাবি ও বিবৃতিকে বিবেচনায় এনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার ১৯৭৩ সালের ৩০শে নবেম্বর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে একটি প্রেসনোট জারি করেন। প্রেসনোটে বলা হয়, “সরকার ১৯৭২ সালের দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৮) অধীনে বিভিন্ন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার পর ঘোষণা করিতেছেন : (১) (ক) এ আদেশের ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০১ ধারা মোতাবেক মওকুফ করা হইল এবং উক্ত আদেশ ব্যতীত অপর কোন আইন বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতারী পরোয়ানা না থাকিলে সেইসব ব্যক্তিকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে; খ) এ আদেশ বলে যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে, উল্লেখিত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে সেসব মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং এ আদেশ ব্যতীত অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের হুলিয়া না থাকিলে তাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে; গ) এ আদেশ বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে অথবা তদন্ত চলিতেছে সেইসব মামলা ও তদন্ত কার্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সব গ্রেফতারী পরোয়ানা অথবা আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ এবং এই আদেশ বলে কোনও ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ থাকিলে ইহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য না হইলে তাহাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে; তবে কোন ব্যক্তি অনুপস্থিতিতে দণ্ডিত হইয়া থাকিলে তাহাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে হাজির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকিবে।
(২) এ আদেশ বলে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (হত্যা), ৩০৪ ধারা (হত্যা চেষ্টা কিন্তু হত্যার শামিল নয়) ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (অগ্নিসংযোগ বা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা ধ্বংসাত্মক কার্য সাধন) ৪৩৬ ধারা (ঘরবাড়ি ধ্বংসের অভিপ্রায়ে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) মোতাবেক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না। সরকারের এ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসে ৩০ হাজার বন্দি ছাড়া পেয়ে যান। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর সাড়ে ঊনিশ মাস আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল। এই সময়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুট-পাট ও অগ্নিসংযোগের দায়ে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী অথবা অন্য কারুর বিরুদ্ধে দালাল আইনে কোনও মামলা হয়নি। যে মামলাগুলো বিচারাধীন ছিল সেগুলোও সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি। এই অপরাধে তখন ৪৬২৩ ব্যক্তি কারাগারে ছিলেন। এদের কারোরই জামায়াত অথবা তার কোনার অঙ্গ সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল না। জামায়াতের যে শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে শেখ হাসিনা সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে যুদ্ধাপরাধের দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের অধীনে বিচারের মুখোমুখি করেছেন, ফাঁসি দিয়েছেন, এ সময় অথবা তারপরে বাংলাদেশের কোনও থানায় কোনও জিডিও হয়নি।
কারাগারে থাকা এ ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা তাদের আত্মীয় ছিলেন কি না জানা যায়নি। ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর দালাল আইন বাতিল করে সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এ অধ্যাদেশ জারির পেছনেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা উত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯ মাসের এবং মোশতাক-জিয়া সরকারের ৫ মাসের অভিজ্ঞতা, সিও ডিসি এমপিদের সুপারিশ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে তৎকালীন সরকারের পক্ষপাতিত্ব বা যুদ্ধাপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রশ্ন যারা তোলেন তারা প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে বুদ্ধি বিবেক হারিয়ে ফেলেছেন বলেই মনে হয়।
কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭ কোটি সন্তানকে ‘মানুষ’ না করে ‘বাঙ্গালী’ করে রাখার জন্য বঙ্গ জননীর কাছে আক্ষেপ করেছিলেন। সম্ভবত বাঙ্গাল মূর্খ হবার কারণে তাদের হাইকোর্ট দেখানো খুবই সহজ কাজ। দালাল, যুদ্ধাপরাধী আর কল্পিত শত্রুদের নির্মূল করার জন্যে আওয়ামী লীগের পর বিএনপি উঠে পড়ে লেগেছে বলে মনে হয়। বিএনপির কিছু নেতা জামায়াত নিষিদ্ধের দাবিও তুলেছেন। দেশের উন্নয়ন এবং নাগরিক দুর্ভোগ কারা লাঘব করবে এ প্রশ্ন এখন অবান্তর হয়ে পড়েছে। ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এ দলটি দিশেহারা করে তুলছে। প্রশ্ন উঠছে, নেতৃত্বহীন বিভ্রান্ত বিএনপি জাতিকেও কি বিভ্রান্ত করতে চায়।