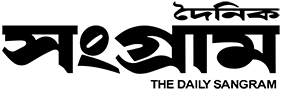বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমস্যা তৈরি হয় ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকেই। তখন একটা সরকার ছিল বটে, কিন্তু সে সরকারের দেশের ওপর বাস্তব কোনও কর্তৃত্ব ছিল না। সবার হাতে অস্ত্র, আর যার হাতে অস্ত্র সে-ই ক্ষমতাবান। যে যেখানে যে রকম ক্ষমতাবান সে সেখানে ততটুকু কর্তৃত্ব ফলিয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে সরকার কার্যকর হয়েছে। তখন সরকার কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে। সরকার ও সরকারি দলের লোকেদের দুর্নীতি, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। এই বিক্ষোভকে দমন করার জন্য সরকার ও সরকার দলীয় লোকেরা বিশেষ করে বিরোধী মতের লোকদের জেল-জুলুম এবং হত্যাকাণ্ডের শিকার বানায়। রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও ক্ষমতা ব্যবহার করে গুম এবং বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এ সময়ই শুরু হয়। তারপর থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই প্রক্রিয়া কম-বেশি সব সময়ই চলেছে, যা বিগত হাসিনা আমলে সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়।
দীর্ঘদিনের এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সাধারণত রাষ্ট্রের উদ্যোগ, সমর্থন, প্রশ্রয়, দুর্বলতা ও অবহেলার কারণেই ঘটে থাকে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় তা-ও ঘটতে পারে রাষ্ট্রেরই কারণে। কিন্তু রাষ্ট্র (রাষ্ট্রের নামে আসলে সরকার) যখন সংগঠিত ও পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তখন তা সকল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং লুটপাটের রাজত্ব কায়েম রাখার জন্য বিরোধী মতকে দমন এবং সমাজে ভয়ের সংস্কৃতি চালু ও বহাল রাখা দরকার হয়। সেই উদ্দেশ্যেই জনসমর্থনহীন সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এই কাজটা করে। সরকার যখন নিজেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে তখন সেটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজে রাষ্ট্রের যেসব প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারি ব্যবহৃত হয় তারা এবং সরকারী দলের নেতা-কর্মী ও সহযোগীরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী স্বার্থেও মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে থাকে। এভাবে সমাজে মাৎস্যন্যায় চালু হয়, অর্থাৎ সবল কর্তৃক দুর্বল নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়। তার মানে হচ্ছে, সরকার বা রাষ্ট্রের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে পারলে সমাজে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধ বা হ্রাস করা সম্ভব।
এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্র বা সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনকে কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়। এ জন্যে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতির দিকে একটু তাকাতে হবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামক যে রাষ্ট্রটি গঠিত হয় তাকে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭২ সালে একটি সংবিধান প্রণীত হয়। উচিত ছিল একটি গণপরিষদের নির্বাচন করে তার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু তা হয়নি। বরং পাকিস্তানের সংবিধান তৈরি করার জন্য নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের জন্য নির্বাচিত সদস্যরা মিলে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করল। নিদেনপক্ষে একটি গণভোট করে এটাকে জায়েজ করা যেত, তা-ও করা হয়নি। ফলে এই সংবিধানকে আইনগত এবং নৈতিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। একটি স্বাধীন জাতির জন্য সেটা অবমাননাকর ব্যাপার। এই নীতিগত প্রশ্ন ছাড়াও এই সংবিধানের আরও অনেক ধরনের ত্রুটি এবং বিচ্যুতি রয়েছে, তার মধ্য থেকে একটি বিষয় এখানে বলা দরকার যে, এতে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এই সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী এতটাই ক্ষমতাধর যে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, বিচার বিভাগ, এমনকি সংসদকেও তার আজ্ঞাবহ থাকতে হয়। প্রকৃতপক্ষে তাকে কোনও জবাবদিহিই করতে হয় না। এভাবে এই সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে বিধিসম্মতভাবেই স্বৈরাচারী ও কর্তৃত্ববাদী করে তোলে। আর যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়, সেজন্যে আর সকলেই তার তাঁবেদারি শুরু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জনপ্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনি, বিচারবিভাগ, মিডিয়া, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন সেক্টরের সুবিধাবাদী লোকজনের চক্র। এভাবে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্রে রেখে একটি কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরাচারী সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। বিশেষ করে এই শাসন যেভাবেই হোক দীর্ঘস্থায়ী হলে তা সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করে। অবস্থা যখন এমন হয় তখন এরা সবাই মিলে ক্ষমতায় থাকা, লুটপাট অব্যাহত রাখা, এবং জনবিক্ষোভ থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করে, ফ্যাসিবাদ কায়েম করে, জনগণের ওপর চরম নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়, এবং সর্বত্র আতঙ্কের রাজত্ব কয়েম করে। এমনটাই ঘটেছিল শেখ হাসিনার পনর বছরের শাসনামলে। তাই, মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্যে প্রথম কাজ হচ্ছে এমন একটা সংবিধান প্রণয়ন করা যা সর্বত্র সবার মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, এবং সবাইকে জবাবদিহিতার আওতায় আনবে। আমাদের বর্তমান সংবিধান সে কাজ করতে ব্যর্থ। এই সংবিধান বহাল রেখে মানবাধিকার রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রীয় বা সরকারী নিপীড়ন ও স্বৈরাচার বন্ধ করা সম্ভব নয়। সে কারণে বর্তমান সংবিধান বাতিল করে দিয়ে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা দরকার। ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পর এই দাবি উঠেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)সহ অধিকাংশ রাজনৈতিক শক্তি এ দাবির সঙ্গে একমত হয়নি। শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই সংবিধান সংস্কারের উদ্যোগ নেয় এবং অনেকগুলো সুপারিশ ও প্রস্তাব উপস্থাপন করে। কিন্তু বিএনপিসহ গুটিকয়েক রাজনৈতিক দল অনেক গুরুত্বপূর্ণ (১২-এর পাতায় দেখুন)
রাষ্ট্রযন্ত্রের মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিকার ও প্রতিরোধ
সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করেনি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিছু সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন একইসঙ্গে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে সেসব সুপারিশ পাশ হবে এবং নির্বাচন-পরবর্তী সরকার সেগুলো সংবিধানে সন্নিবেশ এবং বাস্তবায়ন করবে। এতে ‘নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল’ গোছের কিছু উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।
দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, রাষ্ট্র চালান রাজনীতিকরা, অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলো। এদের কেউ থাকেন রাষ্ট্রক্ষমতায়, কেউ থাকেন তাদের আশেপাশে, কেউ বা থাকেন বিরোধী শিবিরে। সংবিধান, আইন, বিধি, নিয়ম বা নীতি যা-ই বলি না কেন তার প্রয়োগ, বাস্তবায়ন এবং অনুশীলন নির্ভর করে মূলত এবং প্রথমত এই রাজনীতিকদের ওপরই। তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মনন, প্রবণতা এবং আচরণ যদি গণতান্ত্রিক এবং মানবিক না হয় তাহলে সংবিধান বা আইনে যা-ই লেখা থাক তার পুরো সুফল পাওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল এবং নেতা-কর্মীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক আচার-আচরণের প্রচণ্ড অভাব, বরং বিপরীতটাই সুলভ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এমনকি তাদের নিজেদের গঠনতন্ত্রও মানে না। নেতা নির্বাচন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং জবাবদিহিতার যে নিয়ম-নীতিগুলো তাদের গঠনতন্ত্রে লেখা থাকে, তা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন আলাদা, মোদ্দা কথা তা-ও প্রায়শঃই অনুসৃত হয় না। এইসব দলগুলোতে এক ব্যক্তি, বা এক পরিবার, বা এক গোষ্ঠী কর্তৃত্ব চালায়। এদের কর্তৃত্ব এতটাই প্রবল হয় যে অন্যরা তাদের সঙ্গে ভিন্নমত দেখালেও দলে তাদের অবস্থান টলে যায়। রাষ্ট্রীয় বা সরকারী মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে হলে রাজনীতিকদের এই ধরনের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গঠনতন্ত্রের অনুসরণ এবং গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করা দরকার। যে রাজনীতিকরা নিজেদের দলের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রতিনিয়ত অনিয়ম এবং কর্তৃত্ববাদের চর্চা করেন তারা রাষ্ট্রক্ষমতায় গিয়ে গণতন্ত্রের চর্চা করবেন এটা আশা করা যায় না। বরং ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পর তারা আরও বেশি স্বৈরাচারী হয়ে উঠবেন এটাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে থেকেও রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারী আচরণ করতে পিছপা হয় না।
কর্তৃত্ববাদ এবং স্বৈরাচারী মনোভাব আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের জনপ্রশাসন, পুলিশ, বিচার বিভাগসহ সকল জায়গায় সকল স্তরে গভীরভাবে প্রোথিত। একজন সচিব তার জায়গায় অধঃস্তনদের ওপর যে ধরনের কর্তৃত্ব খাটান, একজন ডিসি তার জায়গায় তার অধঃস্তনদের ওপর তার চেয়ে কম ক্ষমতাধর নন। তারা এতটাই কর্তৃত্ববান যে তারা কোনও ভুল করলেও অধঃস্তনরা তার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, ভদ্রভাবে বা বিনয়ের সঙ্গে সে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সাহসও পান না। আমাদের সমাজের সর্বত্রই এই অবস্থা বিরাজমান। সুযোগ পেলেই অনিয়ম করা, কর্তৃত্ব খাটানো, এবং স্বৈরাচারী আচরণ করা আমাদের জাতীয় চারিত্রে পরিণত হয়েছে। আর এই বৈশিষ্ট্যের কারণে আমরা সবাই-ই নিজ নিজ জায়গায় মানবাধিকার লঙ্ঘন করে থাকি। আমরা হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করছি বড় বড় রাজনৈতিক দল নতুন সংবিধান তৈরির পক্ষে তো নয়ই, এমনকি তারা উল্লেখযোগ্য মৌলিক সংস্কারের প্রতিও তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। তার মানে কি এই যে তারা ক্ষমতায় গিয়ে কর্তৃত্ব ফলাতে চায়? স্বৈরাচারী হতে চায়? রাজনীতিক এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক করে তোলার কোনও পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত সরকার, নির্বাচন কমিশন বা রাজনৈতিক দল কারও দিক থেকেই নেওয়া হয়নি। আমরা দেখছি জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর কথা, আচরণ এবং কাজের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আসেনি। একেবারেই তথৈবচ অবস্থা।
রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল কারিগর রাজনীতিকরা, এবং রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের সঙ্গে মেলে রাষ্ট্রযন্ত্রের কুশী-লবরা, এবং অন্যান্যরাওÑ ব্যবসায়ী, মিডিয়া, সংস্কৃতিকর্মী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, সবাই। সাধারণত তাদের জনসমর্থন থাকে না। সুতরাং টিকে থাকার জন্যে তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের নতুন নতুন বিষয়, উপায়-উপকরণ এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করে। তারা সেগুলোকে যৌক্তিক প্রমাণ করার জন্যে নতুন বয়ান নির্মাণ করে। তাদেরকে বিদেশী আধিপত্যবাদী শক্তির আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। সেটা করতে গিয়ে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে হয়। এভাবে স্বৈরাচার, কর্তৃত্ববাদিতা এবং বিদেশী আধিপত্য মিলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক জটিল অন্তর্জাল তৈরি হয়। এই অন্তর্জালকে ছেঁড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম একটি উপায় হলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপযুক্ত বিচার করা। বিগত হাসিনা রেজিম এবং জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় সংঘটিত গুম-খুন, নির্যাতন, গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু হয়েছে, কিন্তু তা অব্যাহত থাকবে কিনা তা নিয়েও সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছে। দু-একটা ব্যতিক্রম বাদে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এই বিচারের প্রতি মোটেও আগ্রহ দেখাচ্ছে না।
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জনসমক্ষে এসেছে। অতীতে প্রতিটি সরকারের আমলেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যদিও পরিমাণ ও মাত্রায় একেক আমলে একেক রকম হয়েছে। বিগত হাসিনা রেজিম রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে কল্পনাতীত রকম নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে মানবাধিকারের কী ভয়াবহ লঙ্ঘন করেছে তা দেখে বিশ্ববাসী বিস্মিত, শিহরিত ও আতঙ্কিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা সব জানলাম, দেখলাম, বুঝলাম, কিন্তু তার প্রতিবিধানের জন্য যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেই তাহলে হাসিনা রেজিমের বিতাড়নের মধ্য দিয়ে টেকসই কোনও অর্জন সম্ভব হবে কি? নাকি ভবিষ্যতেও একই রকম মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথ খোলা থেকে যাবে?
এই পরিস্থিতিতে, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রত্যাশিত উন্নতি হবে একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে এটাও সত্যি যে, মানবাধিকার সুরক্ষার পক্ষে জনসচেতনতা, সক্রিয়তা ও দাবি ক্রমশঃ শক্তিশালী হচ্ছে। হয়তো এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতিকরা এবং রাজনৈতিক দলগুলো সেই জনদাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া না দিয়ে পারবেন না। সেদিন তারা নিজেরাই স্বৈরাচার তৈরির কারখানা বন্ধ করবেন, রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পথকে সঙ্কুচিত করবেন, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিচার নিশ্চিত করবেন। আপাতত এই আশা এবং স্বপ্নই আমাদের সম্বল।