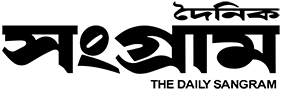মনোয়ারা বেগম
২০২৪ সালের জুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে কারণে তা হলো একটি স্বাধীন দেশে একটি স্বৈরাচারী সরকার শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য কিভাবে দেশের নিরীহ, নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর হত্যাকাণ্ড চালায়।
প্রথমে এটি ছিল সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটার বিরুদ্ধে ছাত্রদের আন্দোলন। কিন্তু পরবর্তীতে আন্দোলন ধীরে ধীরে রূপ নেয় তৎকালীন সময়ে বিদ্যমান স্বৈরাচার সরকারের পতনের জন্য ছাত্র-জনতার একদফা আন্দোলনে। যেখানে দেশের সর্বস্তরের সকল পেশার জনগণ যোগ দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারের পতনের মধ্য দিয়ে ইতিহাস হয়ে ওঠে।
১৯ জুলাই দুপুর তিনটার দিকে আমার বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি উপরে হেলিকপ্টার আর নিচে আওয়ামী লীগের পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা সিটি হাসপাতালের সামনে দাঁড়িয়ে ধারালো অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দিচ্ছে না। আর ছাত্রদের ওপর টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ছুঁড়ছে। আর তখনই দেখি হাসপাতাল থেকে বের হওয়া এক সাধারণ ছাত্রকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে সারা শরীর রক্তাক্ত করে ফেলেছে। ওর পরণে সাদা টি শার্ট ছিল। রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু ওরা থামছিল না। ওই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব ছিল না। তাই আমার সাহেব আর আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়ে ওই ছেলেটার কাছে গিয়ে সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। নয়তো ওকে কুপিয়ে মেরেই ফেলতো।
তার একটু পরই সন্ধ্যার আগে ওই হাসপাতাল থেকে ৩ জন ছাত্র বের হয়ে আসে। তাদের কোলে একটা বাচ্চার লাশ। বাচ্চার মাথার মগজ বের হয়ে গেছে। আওয়ামী লীগের ছেলেরা যখন বাচ্চার লাশটা রেখে দিয়ে ওই ৩ জন সাধারণ ছাত্রকে আক্রমণ করলো ধারালো অস্ত্র দিয়ে। তখন ওরা দৌড়ে পালিয়ে এসে আমার কাছে সাহায্য চাইলে আমি আমার ফ্ল্যাটে ওদের শেল্টার দিই। ওরা একেবারেই নিরস্ত্র আর তখনই আমাদের সাথে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের সরাসরি দ্বন্দ্ব বাধে। ওরা আমাদের বলে, ওই ছাত্রদের বের করে দিতে। ওখানে অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়। ওদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা নিরস্ত্র ছেলেগুলোকে কেন মারছো? ওরা বলল, ওই ছাত্ররা আমাদের ওপর আক্রমণ করেছে। আমি তখন বললাম, ওদের হাতে তো কিছুই নেই আর তোমাদের হাতে তো বড় বড় ধারালো অস্ত্র। ওরা তোমাদেরকে কিভাবে আক্রমণ করেছে? কোনোভাবেই মানতে রাজি নয় তারা। সেখানে অনেকক্ষণ ধরে চলে যুদ্ধ। হার মানিনি আমি। তখন শুধু মনে হয়েছিল একটা কথাই। একদিন তো মরতে হবেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় তবে সেই মৃত্যু অনেক সম্মানের হবে। আর মনে হচ্ছিল ওরা প্রত্যেকে আমার সন্তান। ওদের জায়গায় আমার ছেলে হলে আমি কি করতাম, ওরা কত মহান ওদের মনের বিশালতা পেয়েছি ওই সময়ে। ওরা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল না। ওরা দেখেছে বড় ভাইদের কতটা কষ্ট আর তাই বড় ভাইদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধে নেমেছে। ওরা ওদের মায়ের ভালোবাসা, বাবার নিষেধকে উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে। ওরা একেকজন বীর যোদ্ধা।
তারপর ২৮ জুলাই যখন পঙ্গু ও চক্ষু হাসপাতালে গেলাম ওদের খোঁজ-খবর নিতে, গিয়ে দেখলাম এক ভয়াবহ চিত্র। কোন চিকিৎসা নেই, যত্ন নেই, ওষুধ নেই ও খাবারের মান জঘণ্য। কারণ তখনো হাসপাতালের পরিচালক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে শেখ হাসিনার লোক। বিশাল ভয়ঙ্কর ক্ষত নিয়ে হাসপাতালের বেডে আহতরা কাতরাচ্ছে। তখন ভাবলাম আমি ওদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি। তখন পঙ্গুতে ক্যাজুয়ালিটি-২ এ, ৬০ জন পেসেন্ট ছিল। ডাক্তাররা তাদেরকে প্রতিদিন দশটা ডিম আর বারোটা করে লেবু খেতে বলেছে। তারপর তাদের প্রচুর রক্ত লাগছিল, কারণ ওদের ক্ষত ছিল অনেক মারাত্মক।
সরকারি হাসপাতাল হওয়ার পরও ওদের কাছ থেকে রক্তের জন্য টাকা নিচ্ছিল। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগছিল যে, এরা সবাই ছিল সরকারি স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্র। আর ছিল সাধারণ সিএনজি চালক, রিকশাচালক। ওদের কারোরই সেই রকম আর্থিক অবস্থা ছিল না, হাসপাতালের প্রতিদিনের খাবার ও ওষুধের ব্যবস্থা করা। তখন ভাবলাম যতটুকু পারি ওদের খাবার ও ওষুধের খরচের সহযোগিতা করতে হবে। টানা একমাস ৬০ জনের ওষুধ ও খাবারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছি।
এ সবই করতে হয়েছিল খুব সাবধানে লুকিয়ে। একটা চিন্তাই মাথায় কাজ করছিল, মরতে তো হবেই একদিন। কিছু ভালো কাজ করে যাই। ওই সময় একমাত্র আমি হাসপাতালে যেতাম খাবার নিয়ে, অর্থ সাহায্য নিয়ে।
৪ আগস্ট কারফিউ চলছিল। হাসপাতাল থেকে ওরা আমাকে ফোনে বলছিল, আন্টি আপনি আজকে আইসেন না। আপনার কিছু হয়ে গেলে আমাদের কি হবে? কিন্তু আমি গিয়েছি সকাল ৭টায়। সবাই যখন ঘুমায় তখন আমি ওদের জন্য খাবার দিয়ে নয়টার মধ্যে চলে আসি।
তারপর জাতীয় চক্ষু হাসপাতালে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি আরো মর্মান্তিক দৃশ্য। সেখানে প্রত্যেকটা বেডে শুয়ে আছে পুলিশের গুলিতে অন্ধ হয়ে যাওয়া স্কুল-কলেজের ছাত্র ও সাধারণ কর্মজীবী মানুষগুলো। তাদের সংখ্যা ছিল ১০০০-এর ওপর। হাসপাতালে দায়িত্বরত এক কর্মচারীর ভাষ্য অনুযায়ী ওদের বেশিরভাগেরই এক চোখ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছে। কারো দুই চোখ গুলিবিদ্ধ হয়ে অন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে ছোট একটি ছেলের নাম ছিল, রাশিদুল ও চোখে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর পুলিশ ওকে ১১ দিন জেলহাজতে আটকে রেখেছিল। ফলে চোখে ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল। ৫ আগস্ট ও জেল থেকে ছাড়া পায়। জেলে থাকা অবস্থায় ওদের কয়েকজনের ওপর চলে চরম নির্যাতন। এরপর আমরা যাই নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে। সেখানে যারা ভর্তি ছিল তাদের অবস্থা ছিল চরম সংকটপূর্ণ। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল কোমাতে। তারা ছিল জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।
পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছে। বাকিরা এখনো এক বছর যাবত প্যারালাইজড অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে। কারো গুলি এখনও মাথার ভিতরে রযে গেছে। কারো মাথার খুলি উড়ে গেছে। কারো শরীর ভর্তি, কারো মাথা ভর্তি স্পিন্টার। এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে তার যন্ত্রণা। এই দৃশ্য দেখার পর মনে হয়েছে যদি উনাদের পাশে না দাঁড়াই তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। সারা জীবন নিজেকে স্বার্থপর অপরাধী মনে হবে।
আমার সাথে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন ইব্রাহিমপুর সালাউদ্দিন শিক্ষালয়ের শিক্ষিকা জোবায়দা বেগম। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিচিত মহল থেকে প্রায় ৩০ লাখ টাকা সাহায্য পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে পংগুতে ১০০ জনের মতো, নিউরোতে ১১ জন ও চক্ষু হাসপাতালে ৮৪ জনকে সহযোগিতা করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এছাড়াও আহতরা যেন সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য প্রায় ২২ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সহযোগিতা এখনো অব্যাহত আছে।
জুলাই আন্দোলনে সব ভয়ভীতি উপেক্ষা করে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমার সব সময়ই মনে হয়েছে, ওদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ওরা আমাদের সন্তান বা ভাই। ওরা আমাদের বীর সন্তান। এখনো থামেনি আন্দোলন। এখনো চলছে ২৪ যোদ্ধাদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও দেশ গঠনের আন্দোলন।
এই আন্দোলন তখনই পরিপূর্ণভাবে সফল হবে যখন আমরা এই যোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান দিতে পারবো এবং একটি বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করতে পারব। আর এই কাজে আমাদের প্রত্যেককে অংশ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের সন্তানদের এই বিশাল আত্মত্যাগকে। ভুলে গেলে আমরা বিবেচিত হব অযোগ্য অভিভাবক হিসেবে।
সাবেক অধ্যক্ষ, মিরপুর ইন্টারন্যাশনাল টিউটোরিয়াল।